
আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোটো মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না।
সকালবেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, "বাবা, রামদয়াল দরোয়ান কাককে কৌয়া বলছিল, সে কিচ্ছু জানে না। না?"
সে আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতিদ্রুত উচ্চারণে আগডুম-বাগডুম খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।
আমার ঘর পথের ধারে। হঠাৎ মিনি আগডুম-বাগডুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা।"
ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে, হাতে গোটাদুই-চার আঙুরের বাক্স, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা পথ দিয়া যাইতেছিল তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারত্নের কিরূপ ভাবোদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল।
মিনির চিৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল, অমনি সে ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মতো ছিল যে, ঐ ঝুলিটার ভিতর সন্ধান করিলে তাহার মতো দুটো-চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে।
আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম- সে আমার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে কিসমিস, খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।
কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলায় বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম-কিসমিসে পরিপূর্ণ।
সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতোমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেস্তাবাদাম ঘুষ দিয়া মিনির ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।
দেখিলাম, এই দুটি বন্ধুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে- যথা, রহমতকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার ও ঝুলির ভিতর কী?"
রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, "হাঁতি।"
উহাদের মধ্যে আরও-একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমত মিনিকে বলিত, "খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি কখুনু যাবে না?"
কথাটার একটা কোনো জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাববিরুদ্ধ- সে উল্টিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?"
রহমত কাল্পনিক শ্বশুরের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মুষ্টি আস্ফালন করিয়া বলিত, "হামি সসুরকে মারবে।”
শুনিয়া মিনি শ্বশুর-নামক কোনো-এক অপরিচিত জীবের দুরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।
মিনির মা অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের লোক। রহমত কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন।
একদিন সকালে আমার ছোট ঘরে বসিয়া প্রুফশিট সংশোধন করিতেছি। এমন সময় রাস্তায় ভারি একটা গোল শুনা গেল।
চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমতকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে- তাহার পশ্চাতে কৌতূহলী ছেলের দল চলিয়াছে। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কী?
কিয়দংশ তাহার কাছে, কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিৎ ধারিত- মিথ্যাপূর্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমত তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।
রহমত সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানারূপ অশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময় 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।
রহমতের মুখ মুহূর্তের মধ্যে কৌতুকহাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?”
রহমত হাসিয়া কহিল, "সিখানেই যাচ্ছে।”
সাংঘাতিক আঘাত করার অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।
তাহার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গেলাম।
কত বৎসর কাটিয়া গেল। আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে-না-হইতে সানাই বাজিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।
আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমত আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।
আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই। তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।
কহিলাম, "কী রে রহমত, কবে আসিলি?"
সে কহিল, "কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।"
আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়।
আমি তাহাকে কহিলাম, "আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি কিছু ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও।”
কথাটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না?"
আমি কহিলাম, "আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারও সহিত দেখা হইতে পারিবে না।"
সে যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তারপরে 'বাবু সেলাম' বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।
আমার মনে কেমন একটু ব্যথা বোধ হইল। মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময়ে দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।
কাছে আসিয়া কহিল, "এই আঙুর এবং কিঞ্চিৎ কিসমিস, বাদাম খোঁখীর জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।"
আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, "আপনার বহুৎ দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে- আমাকে পয়সা দিবেন না। বাবু, তোমার যেমন একটি লড়কি আছে, তেমনি

দেশে আমারও একটি লড়কি আছে। আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওদা করিতে আসি না।"
এই বলিয়া সে আপনার মস্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে একটুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু সযত্নে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।
দেখিলাম, কাগজের উপর একটি ছোট হাতের ছাপ। ফটোগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভুসা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণচিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমত প্রতিবৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে।
দেখিয়া আমার চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপুরে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু আমি কিছুতে কর্ণপাত করিলাম না। রাঙাচেলি-পরা কপালে-চন্দন-আঁকা বধূবেশিনী মিনি সলজ্জভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।
তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়ালা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল, "খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি যাবিস?"
কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।
মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তাহার মেয়েটিও ইতোমধ্যে এইরূপ বড় হইয়াছে।
আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, "রহমত, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।"
(সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত)
দরোয়ান -দারোয়ান শব্দের উচ্চারণভেদ।
কাবুল - আফগানিস্তানের রাজধানী।
কাবুলিওয়ালা - কাবুলের অধিবাসী। অতীতে কাবুলের অনেক লোক নানা কাজে এ দেশে নিয়মিত যাতায়াত করত।
দণ্ড - মুহূর্ত।
নভেল - উপন্যাস।
সপ্তদশ - সতেরো।
পরিচ্ছেদ - অধ্যায়।
পার্শ্বে - পাশে।
কন্যারত্ন - -কন্যাকে আদর করে রত্নের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
ভাবোদয় - ভাবের উদয়। মনে চিন্তা বা ভাবনা জাগা।
ঊর্ধ্বশ্বাসে - অতি দ্রুতবেগে।
অন্তঃপুর - বাড়ির ভিতরের অংশ।
অভিপ্রায় - ইচ্ছা।
খোবানি - বাদাম জাতীয় ফল।
দুহিতা - কন্যা।
দ্বার - দরজা।
সমীপস্থ - নিকটে, কাছে।
অনর্গল - অবিরাম, অনবরত।
সহাস্যমুখ - হাসিমুখ।
পঞ্চবর্ষীয় - পাঁচ বছর বয়সী।
প্রুফশিট - কোনো লেখা ছাপার আগে বানান, বাক্য, যতিচিহ্ন এসব সংশোধনের জন্য মুদ্রিত পত্র।
মেওয়া - ডালিম, আঙ্গুর, বাদাম প্রভৃতি ফল। এ গল্পে খুকির জন্যে কাবুলিওয়ালার আনা এ জাতীয় উপহার।
খোঁখী - কাবুলিওয়ালা কর্তৃক 'খুকি' শব্দের অশুদ্ধ উচ্চারণ।
স্বভাববিরুদ্ধ - স্বভাবের বিপরীত।
মুষ্টি আস্ফালন - জোরে মুঠি নাড়িয়ে রাগ প্রকাশের ভঙ্গি।
নিঃসংশয় - শঙ্কাহীন।
কিঞ্চিৎ - অল্প।
ধারিত - ঋণগ্রস্ত।
প্রফুল্ল - আনন্দিত।
লড়কি - মেয়ে।
ভিন্ন সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠলেও মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ ভালোবাসার অনুভূতি অনেকাংশেই এক। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আফগানিস্তানের মরু পর্বতের রুক্ষ প্রকৃতিতে গড়ে ওঠা একজন পিতা এবং নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার একজন বাঙালি পিতার ভিতরের স্নেহপ্রবণ মনের ঐক্য সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। দেশকালের সীমারেখা পিতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবণতায় কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। যে দেশের, যে সময়ের বা যে সংস্কৃতিরই মানুষ হোক না কেন পিতা সব সময়ই তার সন্তানকে একই রকমভাবে ভালোবাসেন। সন্তানের মঙ্গলচিন্তা সব পিতারই সহজাত আকাঙ্ক্ষা। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বের সকল পিতার পিতৃত্বের সর্বজনীন ও চিরন্তন রূপ উন্মোচিত করেছেন।
এশীয়দের মধ্যে যিনি প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বসভায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি হলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে (২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর হয়নি। সতেরো বছর বয়সে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন; কিন্তু পড়া শেষ না হতেই দেশে ফিরে আসেন তিনি। কিন্তু স্বশিক্ষা ও সাধনার একক অবদানে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এত সমৃদ্ধ করেছেন যার কোনো তুলনা নেই। কাব্য, ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সংগীত- সাহিত্যের সকল শাখা তাঁর আশ্চর্য অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ এবং চিত্রকলাতেও তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন।
অনন্যসাধারণ তাঁর প্রতিভা। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, সুরকার, গীতিকার, নাট্যকার, নাট্যপ্রযোজক এবং অভিনেতা। শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তিনি শিক্ষায় নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের একটি দেশপ্রেমমূলক গান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। রবীন্দ্রনাথের লেখা গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর বিভিন্ন রচনা সংকলিত হয়েছে 'কৈশোরক' নামে একটি সংকলনে।
১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
ক. সাধু রীতিতে লেখা ১০টি গল্পের তালিকা তৈরি কর (একক কাজ)।
খ. পাঠ্য বইয়ের ১টি করে সাধু ও চলিত রীতির গদ্য অবলম্বনে রীতি দুটোর ৫টি পার্থক্য বের কর (দলীয় কাজ)।
গ. সাধু রীতির একটি অনুচ্ছেদ চলিত রীতিতে রূপান্তর কর।
১. 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে শঙ্কিত স্বভাবের মানুষটি কে?
ক. রহমত
খ. মিনির মা
গ. রামদয়াল
ঘ. মিনির বাবা
২. মিনির বাবার মনে একটু ব্যথা বোধ হয়েছিল কেন?
ক. মিনি শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছে বলে
খ. রহমতকে কারাগারে যেতে দেখে
গ. মিনির সাথে রহমতের দেখা না হওয়ায়
ঘ. রহমতের মেয়ের কথা ভেবে
উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
ফাতেমা চৌধুরী অফিসে যাওয়ার পথে প্রায়ই একটি পথশিশুকে রাস্তায় শুয়ে থাকতে দেখেন। একদিন তিনি ছেলেটিকে কিছু খাবার দিতে চাইলে সে ভয়ে পালিয়ে যায়। কয়েকদিনের চেষ্টায় ছেলেটি তার সাথে নানা গল্পে মেতে ওঠে। এখন প্রায়দিনই তিনি ছেলেটির জন্য বাসায় তৈরি খাবার নিয়ে আসেন। কখনো তার দেখা না পেলে খুব চিন্তিত হয়ে ওঠেন।
৩. উদ্দীপকের ফাতেমা চৌধুরীর সাথে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের কোন চরিত্রের মিল আছে?
ক. রহমত
গ. লেখক
খ. রামদয়াল
ঘ. মিনি
৪. উদ্দীপকে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের কোন দিকটি ফুটে ওঠেছে?
i. সন্তান-বাৎসল্য
ii. সহমর্মিতা
iii. সহযোগিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উদ্দীপক-১: নতুন দারোয়ান সামাদ মিয়ার সাথে ছেলের বেশি ভাব-বন্ধুত্ব কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না আবীরের মা। তিনি স্বামীকে বোঝান- বিভিন্ন ফন্দি করে অনেক মানুষ এখন অন্যের বাচ্চা চুরি করে। সামাদ মিয়াও তো একদিন তেমন কিছু করে বসতে পারে।
উদ্দীপক-২: বারো বছর আগের ছোট্ট আবীর আজ কলেজ থেকে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় হাসপাতালে। রক্তের জন্য বাবা-মা বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করছেন। খবর পেয়ে সামাদ মিয়া ছুটে এসে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলেন ‘সাহেব, আবীর বাবার জন্য আমার সব রক্ত নেন, আমার নিজের ছেলেরে হারাইছি, ওরে হারাইলে আমি বাঁচুম না।’
ক. কাবুলিওয়ালার মলিন কাগজটিতে কী ছিল?
খ. 'আমিতো সওদা করিতে আসি না।' কথাটি বুঝিয়ে লেখ।
গ. উদ্দীপক-১ অংশে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'উদ্দীপকের সামাদ মিয়া যেন কাবুলিওয়ালা গল্পের মূল ভাবকেই ধারণ করে আছে।'- বিশ্লেষণ কর।

লখার রাতের বিছানা ফুটপাতের কঠিন শান। এই শান দিনের বেলায় রোদে পুড়ে গরম হয়। রাতে হিম লেগে বরফের মতো ঠান্ডা হয়। ঠান্ডা শানে শুয়ে লখার বুকে কাশি বসে। গায়ে জ্বর ওঠে।
বাপকে লখা দেখেনি। চেনে না। মা তার ত্যানাখানি পরে দিনভর কেঁদে-কেঁদে ভিখ মেঙে ফেরে। লখার দিন কাটে গুলি খেলে, ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে মারামারি করে আর খাবারের দোকানের এঁটোপাতা চেটে। রাতে মায়ের পাশে লখা খিদের কষ্ট ভুলে যায়।
এই লখা, ছায়া দেখলে বুক কাঁপে যার, সে আজ ভোররাতে মায়ের পাশ থেকে উঠে পড়ল। মা মুখ হাঁ করে ঘুমুচ্ছে। লখা চুপি চুপি পা ফেলে হারিয়ে গেল ধোঁয়া-ধোঁয়া কুয়াশার মধ্যে।
খানিকটা এগিয়ে উঁচু রেললাইন যেন দুটো মরা সাপ। পাশাপাশি শুয়ে আছে চুপচাপ। লখা ইটের টুকরো দিয়ে ইস্পাতের লাইনে ঠুক-ঠুক ঠুকে তার উপর কান পাতল। হ্যাঁ, শব্দ শোনা যাচ্ছে। যেন গানের সুরলহরি বয়ে যাচ্ছে কানের ভিতর দিয়ে। লখা ভারি মজার দুষ্টু ছেলে। গানের মজা ফুরিয়ে গেলে পর এক লাফে লাইন পেরিয়ে ওপারে পৌঁছে গেল। সেখানে মস্ত নিচু খাদ। তার ভিতর গড়িয়ে পড়লে হাত-পা ভাঙবে নির্ঘাত। খুব সাবধানে খাদ পেরিয়ে ওপারের ডাঙায় উঠে এলো সে। ডাঙাটা আসলে বনজঙ্গলে অন্ধকার। ঝিঁঝি পোকা ডাকছে আর ধেড়ে ধেড়ে গাছের ঝাঁকড়া ছায়া মাথা নেড়ে নেড়ে ভয় দেখাচ্ছে লখাকে।
খচ করে কাঁটা ঢুকে গেল বাঁ পায়ে। কীসের কাঁটা? হবে হয়তো বাবলা-টাবলার। লখা উবু হয়ে বসে কাঁটাটা খসিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলো। কিন্তু বিষ তো যায় না। কী অসহ্য যন্ত্রণা! আঁ আঁ বলে কেঁদে দিল লখা। কিন্তু কাঁদলে তো চলবে না। সময় নেই আর। তাকে যে যেতেই হবে। আবছা অন্ধকার। ফিনফিনে ঠান্ডা।
গাছের পাতা বেয়ে শিশির গড়িয়ে পড়ছে। খুক খুক করে কাশি আসছে লখার। খালি গা শিশিরে ভিজে শীত লাগছে। একটা ছ্যাঁচড়া ডাল লখার হাফপ্যান্টটা টেনে ধরেছে পিছন দিক দিয়ে। প্যান্ট আধখসা অবস্থায় দৌড়াতে লাগল সে।
একটা খেঁকশেয়াল বুঝি তাকিয়ে দেখছিল তাকে। দেখুক গে। এখন ভয় ভয় করলে দেরি হয়ে যাবে। কাজেই এবার চোখ-কান বুজে দৌড় শুরু করতে হলো তাকে। আর শেষটায় সেই অদ্ভুত গাছটার নিচে পৌঁছে গেল লখা, যার ডালে ডালে রক্তের মতো টুকটুকে লাল ফুল। দিনের বেলায় রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে থোকা থোকা ফুলের লাল ঝুঁটির পানে তাকিয়ে থাকে সে। এখন ওই উপরের এক থোকা ফুল তার পেড়ে আনা চাই।
হাতের মুঠো পাকিয়ে মনটাকে শক্ত করে নিল লখা। তারপর চড় চড় করে গাছে উঠে গেল। একেবারে কাঠবেড়ালির বাচ্চা যেন। মগডালের কাছাকাছি এসে কয়েকটা তুলোমিঠের মতো বড়ো বড়ো থোকা পেয়ে গেল সে। শিশিরে ভেজা তুলতুলে। তা হোক, তোমরা এখন আমার। নাও সব টুপটাপ নেমে এসো তো আমার মুঠোর মধ্যে। কষ্ট লাগছে। আহা! কীসের কষ্ট? এই তো একটু পরে আমি তোমাদের এমন একটা উঁচু জায়গায় নিয়ে রেখে দেবো, যেখান অবধি তোমরা এই গাছের মগডালে কোনোদিন উঠতে পারবে না। এসো, এসো, লক্ষ্মীসোনারা সব নেমে এসো তো।
ফুল নিয়ে যখন মাটিতে নেমে এলো লখা, তখন সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে তার। কনুই ও বুকে চটচটে ঠান্ডা। হাত দিয়ে টের পায়, টাটকা রক্ত। গাছের ডালপালা কাঁটায় ভর্তি। গা-হাত-পা ছিঁড়ে গেছে আঁচড় লেগে। তাতে কী! জিতে গেছি আমি। গর্বে বুক ফুলে ওঠে লখার।
সেদিন সকাল ছিল বড় আশ্চর্য সুন্দর। আকাশে হালকা কুয়াশা। অল্প অল্প শীত। আর দক্ষিণের সামান্য বাতাস। পথে পথে মিছিলের ঢল নেমেছে। শত শত মানুষ। হাতে ফুলের গুচ্ছ। ঠোঁটে প্রভাতফেরির গান। ধীর পায়ে শহিদ মিনারের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই ভিড়ের মধ্যে ক্ষুদে টোকাই লখাকে ঠিকই দেখা যাচ্ছে। তাকে চিনতে কষ্ট হয় না। কারণ মিছিলের সবার গায়ে চাদর, কোট, সোয়েটার। শুধু তার গা খোলা উদাম, গাঢ় কালো। হাত উপচে পড়ছে রক্তলাল ফুলের গুচ্ছ। মিছিলে পা মিলিয়ে সেও চলেছে শহিদ মিনারে ফুল দিতে। সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গেয়ে চলছে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি? কিন্তু তার গলা দিয়ে কথা তো ফোটে না, শুধু শব্দ হয় আঁ আঁ আঁ আঁ।
আসলে কথা ফুটবে কী করে! লখা যে জন্মবোবা। বাংলা বুলি তার মুখে ফুটতে পায় না। সে মনে মনে বলে অআকখ। বাইরে শব্দ হয় - আঁ আঁ আঁ আঁ।
শান - পাথর। এখানে কংক্রিটে তৈরি ফুটপাথ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে।
ত্যানাখানি - পুরোনো ছেঁড়া কাপড়।
ভিখ - ভিক্ষা, খয়রাত।
মেঙে - চেয়ে।
গুলি খেলা - মার্বেল দিয়ে খেলা।
ছায়া দেখলে বুক কাঁপে যার - যে নিজের ছায়াকেও ভয় পায়। খুব ভীতু।
বিষ - যে পদার্থ শরীরে ঢুকলে যে কোনো প্রাণী অসুস্থ হয়, কখনো কখনো মারাও যায়। এখানে পথে কাঁটা ফোটার জন্য 'ব্যথা' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।
তুলোমিঠে - তুলোর মতো দেখতে মিষ্টি খাদ্য বিশেষ। একে 'হাওয়াই মিঠাই' ও বলে।
মগডাল - গাছের সবচেয়ে উঁচু ডাল।
গাঢ় - ঘন।
প্রভাতফেরি - ভোরবেলা দল বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় গান গেয়ে সবাইকে জাগিয়ে তোলার অনুষ্ঠান বিশেষ। কিন্তু বাংলাদেশে প্রভাতফেরি একটি বিশেষ অর্থ বহন করে। ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহার করার দাবিতে আন্দোলন হয়। তখন ছিল পাকিস্তান। তখনকার সরকার সে-দাবি মানেনি। তখন ছাত্র-জনতা তীব্র আন্দোলন করতে থাকে। সেই আন্দোলন চরমে ওঠে ১৯৫২ সালে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র-জনতার মিছিলে তৎকালীন সরকারের পুলিশ গুলি চালায়। তাতে শহিদ হন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ আরও অনেকে। তারই স্মরণে প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রভাতফেরি করা হয়। প্রভাতফেরির সময় সকলের কণ্ঠে থাকে আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত এবং শহিদ আলতাফ মাহমুদের সুর করা গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'।
শহিদ মিনার - শহিদের স্মৃতি রক্ষার জন্য নির্মিত মিনার। ভাষা-আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সন্নিকটে আমাদের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার অবস্থিত।
গল্পটিতে একুশে ফেব্রুয়ারির অবিনাশী প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। অতি সাধারণ এক কিশোর লখা। কথা বলতে পারে না সে। কিন্তু তাতে কীই-বা আসে যায়। লখা উঁচু ডালে উঠে লাল ফুল সংগ্রহ করে শহিদ মিনারে যায় শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। কথা বলতে না পারলেও তার মুখ দিয়ে আঁ আঁ আঁ আঁ ধ্বনির মধ্য দিয়েই বেরিয়ে আসে বাঙালির গর্বের উচ্চারণ- 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'।
বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুবকর সিদ্দিক ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে বাগেরহাট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো 'জলরাক্ষস', 'খরাদাহ', 'একাত্তরের হৃদয়ভস্ম', 'বারুদ পোড়া প্রহর' ইত্যাদি।
ক. শহিদ দিবসের ওপর শিক্ষার্থীরা আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।
খ. শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটিকা ইত্যাদির সমন্বয়ে দেয়ালিকা প্রকাশ করবে।
১. লখা কখন তার খিদের কষ্ট ভুলে যায়-
ক. ঘুমুতে গেলে
খ. মাকে কাছে পেলে
গ. খেলার সঙ্গী পেলে
ঘ. প্রভাতফেরির গান শুনলে
২. লখাকে চোখ-কান বুজে দৌড় শুরু করতে হলো, কারণ-
ক. সে ভয় পেয়েছিল
খ. বাইরে অন্ধকার ছিল
গ. তাকে ফুল আনতে হবে
ঘ. মায়ের কাছে ফিরে যেতে হবে
উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
বাবার সাথে প্রভাতফেরিতে এসেছে দিপু। ওর হাতে একটা টকটকে লাল গোলাপ। ওর কন্ঠে গানের সুর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো'। ও লাল গোলাপটিকে শহিদ মিনারের সবচেয়ে উঁচু সিঁড়িতে রাখতে চায়।
৩. লখা ও দিপুর মধ্যে যে বিষয়ে মিল আছে তা হলো-
ক. শহিদ মিনারে আসা মানুষ দেখার ইচ্ছা
খ. শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর আবেগ
গ. প্রতিবন্ধকতা দূর করার অদম্য বাসনা
ঘ. শহিদ দিবসের গান গাওয়ার আগ্রহ
৪. দিপু ও লখা দুজনেই শহিদ দিবস উদযাপন করেছিল; তবু লখাই প্রমাণ করেছে যে-
i. ভালোবাসার অনুভূতি প্রতিবন্ধকতার চেয়ে শক্তিশালী
ii. আত্মবিশ্বাস দ্বারা বাধাকে অতিক্রম করা যায়
iii. শিশুরা অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. iও ii
খ. iও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
১. ইশতিয়াক এবার বৃত্তি নিয়ে জাপানে লেখাপড়া করতে চলে আসায় শহিদ দিবস উদ্যাপন করতে পারবে না। অথচ প্রতিবছর সে প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করত- বক্তৃতা, আবৃত্তি, আলোচনা শুনত, সে-কথা মনে করে তার চোখ জলে ভরে আসে। মনে মনে কিছু করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করে। অতঃপর ইশতিয়াক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও এর ইতিহাস সহপাঠীদের কাছে তুলে ধরার পরিকল্পনা করে।
ক. লখা রাতে কোথায় ঘুমায়?
খ. 'জিতে গেছি আমি। গর্বে বুক ফুলে ওঠে লখার।'- কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
গ. 'লখা ও ইশতিয়াক দুজনের কাছে শহিদ দিবস ভিন্ন আঙ্গিকে এসেছে।'- ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'ইশতিয়াকের শহিদ দিবস উদ্যাপনের আকাঙ্ক্ষা লখার শহিদ দিবস উদ্যাপনের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন।'- বিশ্লেষণ কর।
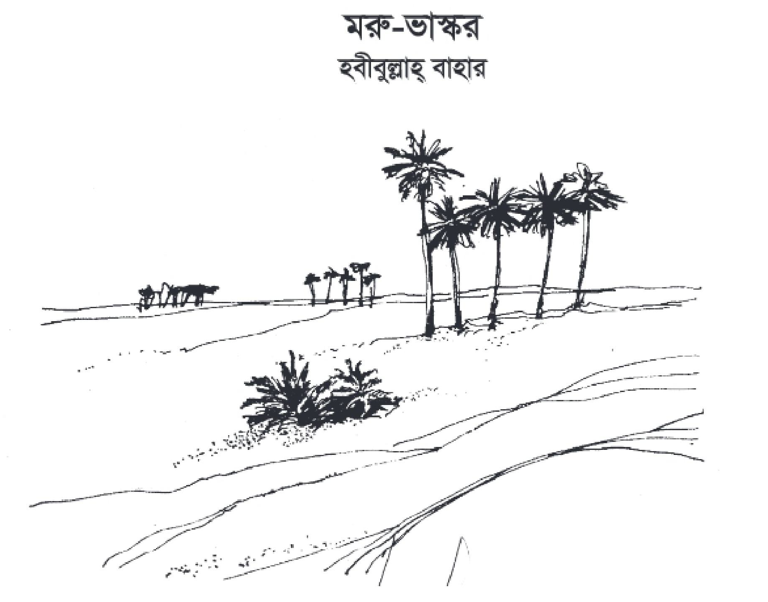
যেসব মহাপুরুষের আবির্ভাবে পৃথিবী ধন্য হয়েছে মানুষের জীবনে যাঁরা এনেছেন সৌষ্ঠব, ফুটিয়েছেন লাবণ্য, মরুভাস্কর হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (স.) তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।
হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবন আলোচনা করতে গিয়ে সকলের আগে আমাদের চোখে পড়ে তাঁর ঐতিহাসিকতা। হজরতের জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিবরণ যেভাবে রক্ষা করা হয়েছে, সত্যের কষ্টিপাথরে ঘষে যেভাবে যাচাই করা হয়েছে, পৃথিবীর কোনো মহাপুরুষের বেলায় তা করা হয়নি।
আরবের লোকের স্মৃতিশক্তি ছিল সত্যি অসাধারণ। বিরাট বিরাট কাব্যগ্রন্থ সহজেই তারা মুখস্থ করে ফেলত। আরবি সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, মুখস্থ না করে কোনো কিছু লিখে রাখা আরবিরা লজ্জার কথা বলে মনে করত। সাহাবিরা এবং অন্য হাদিসজ্ঞরা অনেকেই হাজার হাজার হাদিস মুখস্থ করে রাখতেন।
হজরত মোস্তফা (স.) মানবতার গৌরব। আল্লাহর নবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষই মনে করতেন এবং সেভাবেই তিনি জীবনযাপন করেছেন। ৬৩ বছরের ক্ষুদ্র পরিসর জীবনে হজরতকে কত পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হয়েছে, দেখলে অবাক হতে হয়। যিনি ছিলেন এতিম, তিনি হয়েছিলেন সারা আরবভূমির অবিসংবাদিত নেতা। হজরত যখন মদিনার অধিনায়ক, তখন তাঁর ঘরের আসবাব ছিল একখানা খেজুর পাতার বিছানা আর একটি পানির সুরাহি। অনেক দিন তাঁকে অনাহারে থাকতে হত এবং অনেক সময় উনুনে জ্বলত না আগুন।
হজরতের চরিত্রে সংমিশ্রণ হয়েছিল কোমল আর কঠোরের। বিশ্বাসে যিনি ছিলেন অজেয়, অকুতোভয়, সত্যে ও সংগ্রামে যিনি বজ্রের মতো কঠোর, পর্বতের মতো অটল, তাঁকেই আবার দেখতে পাই- কুসুমের চেয়েও কোমল। বন্ধু-বান্ধবের জন্য তাঁর প্রীতির অন্ত নেই মুখ তাঁর সব সময় হাসিহাসি, ছেলেপিলের সঙ্গে মেশেন তিনি একেবারে শিশুর মন নিয়ে পথে দেখা হলে বালক-বন্ধুকে তার বুলবুলির খবর জিজ্ঞেস -করতে তাঁর ভুল হয় না। বন্ধুবিয়োগে চক্ষু তাঁর অশ্রুসিক্ত হয়। বহু দিন পর দাই-মা হালিমাকে দেখে 'মা আমার, মা আমার' বলে তিনি আকুল হয়ে ওঠেন। মক্কাবিজয়ের পর সাফা পর্বতের পাদদেশে বসে হযরত বক্তৃতা করছিলেন। একজন লোক তাঁর সামনে এসে ভয়ে কাঁপতে লাগল। হজরত অভয় দিয়ে বললেন: "ভয় করছ কেন? আমি রাজা নই, কারও মুনিবও নই এমন মায়ের সন্তান আমি, শুষ্ক খাদ্যই যাঁর আহার্য।”
হজরত জীবনে কাউকে কড়া কথা বলেননি কাউকে অভিসম্পাত দেননি। আনাস নামক এক ভৃত্য দশ বছর হজরতের চাকরি করার পর বলেছেন এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে হজরতের মুখে তিনি কড়া কথা শোনেননি কখনো। মক্কায় বা তায়েফে অত্যাচারে জর্জরিত হয়েও হজরতের মুখে অভিসম্পাতের বাণী উচ্চারিত হয়নি। বরং তিনি বলেছেন, "এদের জ্ঞান দাও প্রভু এদের ক্ষমা করো।"
জগতে সাম্যের প্রতিষ্ঠা মোস্তফা চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও দাস-ব্যবসায়ের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মানবাত্মা যখন গুমরে মরছিল, রাসুলুল্লাহ্ (স.) তখন প্রচার করেন সাম্যের বাণী।
সমগ্র জীবন দিয়ে তিনি সাম্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। চরম দুরবস্থার হাত থেকে দাসদের পরিত্রাণের জন্যও তিনি কাজ করেছেন। মানুষকে সালাতে আহ্বান করার জন্যে মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করেছেন হাবশি গোলাম হজরত বেলালকে।
নারীর অবস্থার পরিবর্তন এনেছেন হজরত। নারীর মর্যাদা ছিল তাঁর শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। তাঁর কন্যা হজরত ফাতেমা (রা.)-কে কেন্দ্র করে সে যুগে গড়ে উঠেছে নারীত্বের আদর্শ। হজরত ঘোষণা করেছেন: “বেহেশত মায়ের পায়ের নিচে।”
কুসংস্কারকে হজরত কোনো দিনই প্রশ্রয় দেননি। একবার হজরতের পুত্রের মৃত্যুদিনে সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। লোকে বলাবলি করতে থাকে বুঝি হজরতের বিপদে প্রকৃতি শোকাবেশ পরিধান করেছে। তখনি সভা ডেকে হজরত এই বাস্তবতাবিরোধী কথার প্রতিবাদ করলেন; বললেন, “আল্লাহ্র বহু নিদর্শনের মধ্যে দুটি চন্দ্র ও সূর্য। কারুর জন্ম বা মৃত্যুতে চন্দ্র সূর্যে গ্রহণ লাগতে পারে না।”
হজরত জ্ঞানের ওপর জোর দিয়েছেন সব সময়। জ্ঞান যেন হারানো উটের মতো তাকে তিনি খুঁজে বের করতে বলেছেন যেখান থেকেই হোক। আরও বলেছেন তিনি: “জ্ঞানসাধকের দোয়াতের কালি শহিদের লহুর চাইতেও পবিত্র।”
এভাবে জ্ঞানের আলোয় মানুষের হৃদয় উজ্জ্বল করার প্রেরণা দিয়ে গেছেন তিনি।
(সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত)
মরু-ভাস্কর- মরুভূমির সূর্য। এখানে হজরত মুহাম্মদ (স.)-কে বোঝানো হয়েছে।
সৌষ্ঠব- সুগঠন।
হাদিস- হজরত মুহাম্মাদ (স.)-এর অনুমোদিত বাক্য ও কাজের সমষ্টি।
কষ্টিপাথর- ঘষে সোনা পরীক্ষা করার এক রকম কালো পাথর।
সুরাহি- পানির এক রকম পাত্র, সোরাই, জলের কুঁজো।
অকুতোভয়- যার কোনো কিছুতে ভয় নেই, নির্ভীক।
অভিসম্পাত- অভিশাপ।
পরিত্রাণ- মুক্তি।
হাবশি গোলাম- আবিসিনিয়ায় (বর্তমানে ইথিওপিয়া) জন্মগ্রহণকারী ক্রীতদাস।
লহু- রক্ত।
'মরু-ভাস্কর' প্রবন্ধে লেখক মহানবির জীবন ও আদর্শের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন যা আমাদের ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিকতার বিকাশে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে।
হজরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সেই মহাপুরুষদের মধ্যে একজন যিনি চরিত্রবান; মানবপ্রেমে, জীবপ্রেমে মহীয়ান। বিপদে ধৈর্যশীলতা, দারিদ্র্যে অচঞ্চলতা, শত্রুর প্রতি ক্ষমাশীলতার মহৎ দৃষ্টান্তে তাঁর জীবন সমুজ্জ্বল। অনেক মহাপুরুষের জীবন প্রকৃত তথ্যের চেয়ে কাল্পনিক নানা তথ্যে ভরা। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনের যত তথ্য পাওয়া যায় সবই ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে স্বীকৃত।
আল্লাহর মহান নবি হওয়া সত্ত্বেও হজরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন একজন সাধারণ মানুষের মতো। তাই তিনি মানবজাতির গৌরব।
তাঁর ৬৩ বছরের ঘটনাবহুল জীবনে, নানা পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁর জীবনের মূলধারা ছিল অপরিবর্তিত। তিনি সব সময় সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন করেছেন। তাঁর চরিত্রে মিশে ছিল হাসিখুশি ভাব, কোমলতা ও কঠোরতা। আপন বিশ্বাসে, সত্যের জন্য সংগ্রামে তিনি ছিলেন বজ্রের মতো কঠোর, পর্বতের মতো অটল। কিন্তু নারী-পুরুষ, বন্ধুবান্ধব, শিশু, কিশোর, আত্মীয়স্বজন সবার সঙ্গে ব্যক্তিগত আচরণে তিনি ছিলেন কুসুমের মতো কোমল। তাঁর চরিত্র ছিল প্রীতিতে, ম
মতায়, স্নেহে, সৌজন্যে দয়ার আধার। জীবনে কাউকে তিনি কড়া কথা বলেননি, কাউকে অভিসম্পাত দেননি। নিজে নির্যাতিত হয়েও প্রতিদানে তিনি ক্ষমা করেছেন।
হজরত মানুষে মানুষে ভেদাভেদের পরিবর্তে সাম্যের বাণী প্রচার করে গেছেন। তিনি চরম দুরবস্থা-কবলিত ক্রীতদাসের পরিত্রাণের জন্য কাজ করে গেছেন। নারীর অবস্থার পরিবর্তন ও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। অন্য ধর্মের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার ও সহিষ্ণু।
হজরত কুসংস্কারকে কখনো প্রশ্রয় দেননি। যা সত্য, যা যুক্তিগ্রাহ্য, তার পক্ষেই তিনি অবস্থান নিয়েছেন। হজরত জ্ঞানচর্চার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন সব সময়। এর ফলে মুসলিম সমাজ জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েছে।
হবীবুল্লাহ্ বাহার ছিলেন কবি নজরুলের 'ভক্তশিষ্য' এবং চিন্তা ও কর্মে পুরোপুরি মানবতাবাদী। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। মূলত প্রবন্ধকার হলেও তিনি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন 'ওমর ফারুক', 'আমীর আলী' ইত্যাদি। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ই এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
ক. মহামানবদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে তাঁদের অনুসরণে ৫টি কল্যাণকর কাজের তালিকা তৈরি কর।
১. হজরত মুহাম্মদ (স.) কোন ক্ষেত্রে বজ্রের মতো কঠোর ছিলেন?
ক. গভীর আত্মবিশ্বাসে
খ. নারীর মর্যাদা রক্ষায়
গ. সত্য ও সংগ্রামের চেতনায়
ঘ. সাম্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায়
২. 'এদের জ্ঞান দাও প্রভু এদের ক্ষমা কর।'-উক্তিটির মধ্য দিয়ে হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রাধান্য পেয়েছে?
ক. ক্ষমা ও মহানুভবতা
খ. দয়া ও করুণা
গ. প্রেম ও ভালোবাসা
ঘ. বাৎসল্য ও ন্যায়বিচার
৩. 'কারুর জন্ম বা মৃত্যুতে চন্দ্র-সূর্যে গ্রহণ লাগতে পারে না।'- উক্তিটির মধ্য দিয়ে হজরতের কোন ধরনের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?
ক. সাম্যবাদিতার
খ. মানবপ্রেমের
গ. সংস্কারমুক্তির
ঘ. দৃঢ়বিশ্বাসের
৪. কোন দৃষ্টিকোণ থেকে আরবের লোকেরা ছিল অসাধারণ?
ক. সহিংসতার
খ. ধৈর্যের
খ. পেশিশক্তির
ঘ. স্মৃতিশক্তির
১। হজরত মুহাম্মদ (স.) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের কোনো অহমিকা তাঁর ছিল না। মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অফুরন্ত। সকলের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল হাসিমাখা। ছোটো শিশুদের তিনি খুব বেশি স্নেহ করতেন। তাঁর বালক-বন্ধুর সাথে দেখা হলে তিনি বন্ধুর বুলবুলি পাখির খবর নিতেও ভুলে যেতেন না।
ক. হজরত মুহাম্মদ (স.) কোন ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন?
খ. শহিদের রক্তের চেয়ে জ্ঞানসাধকের কলমের কালিকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলার কারণটি ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকে হজরত মুহাম্মাদ (স.)-এর যে গুণটি ফুটে উঠেছে তা 'মরু-ভাস্কর' প্রবন্ধের আলোকে বর্ণনা কর।
ঘ. "উদ্দীপকটিতে হজরত মুহাম্মাদ (স.)-এর গুণাবলির আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।"-বক্তব্যটির যৌক্তিকতা 'মরু-ভাস্কর' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

কবিতা কাকে বলে, বলা খুব মুশকিল। কিন্তু আমরা যারা পড়তে পারি, তারা কম-বেশি কবিতা চিনি। কবিতারও চেহারা আছে। বইয়ে বা পত্রিকায় যে-লেখাগুলো খুব সুন্দরভাবে ছাপানো হয়, যে-লেখাগুলো, পঙ্ক্তিগুলো খুব বেশি বড় হয় না, যে-গুলোতে একটি পঙ্ক্তি আরেকটি পঙ্ক্তির সমান হয়, সে-লেখাগুলোই কবিতা। যে-লেখাগুলো পড়লে মন নেচে ওঠে; গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, চোখে বুকে রং-বেরঙের স্বপ্ন এসে জমা হয়, তা-ই কবিতা। যা পড়লে, দু-তিনবার পড়লে আর ভোলা যায় না, মনের ভেতর যা নাচতে থাকে, তা-ই কবিতা।
কবিতা কারা লেখেন? কবিরা লেখেন কবিতা। তাঁরা একটি শব্দের পাশে আরেকটি শব্দ বসিয়ে, একটি শব্দের সাথে আরেকটি শব্দ মিলিয়ে কবিতা লেখেন। আমরা যদি কিছু বানাতে চাই, তাহলে কিছু-না-কিছু জিনিস লাগে। উপমা একটি ঘুড়ি বানাতে চায়। ঘুড়ি বানানোর জন্যে উপমার দরকার লাল-নীল কাগজ, সুতো, বাঁশের টুকরো। মৌলি একটি পুতুল বানাতে চায়। তার দরকার হলদে টুকরো কাপড়, সুতো, তিনটা লাল বোতাম, দুটো সবুজ কাঁটা, একটু তুলো। তেমনি কবিতা বানাতে হলেও জিনিস চাই। কবিতার জন্যে দরকার শব্দ - রংবেরঙের শব্দ। 'পাখি' একটা শব্দ, 'নদী' একটা শব্দ, 'ফুল' একটা শব্দ, 'মা' একটা শব্দ; এমন হাজারো শব্দের দরকার হয় কবিতা লেখার জন্যে। কবি হতে পারে কে? সে-ই হতে পারে কবি, যে লিখতে পারে কবিতা, যার ভালোবাসা আছে শব্দের জন্যে। যে শব্দকে ভালোবাসে খুব, শব্দকে আদর করে করে যে খুব সুখ পায়, সে-ই হতে পারে কবি। কবিরা গোলাপের মতো সুন্দর সুন্দর কথা বলেন, চাঁদের মতো স্বপ্ন দেখেন। তুমিও গোলাপের মতো সুন্দর কথা বলতে চাও, চাঁদের মতো স্বপ্ন দেখতে চাও? তোমার যদি শব্দের জন্যে আদর-ভালোবাসা না থাকে, তাহলে পারবে না তুমি গোলাপের মতো লাল গন্ধভরা কথা বলতে, চাঁদের মতো জ্যোৎস্নাভরা স্বপ্ন দেখতে।
তুমি কি লিখতে চাও ফুলের মতো কবিতা? বানাতে চাও নূপুরের শব্দের মতো ছড়া? যদি চাও তবে তোমাকে সারাদিন ভাবতে হবে শব্দের কথা। খেলতে হবে শব্দের খেলা। নানান রকমের শব্দ আছে আমাদের ভাষায়। তোমাকে জানতে হবে সে-সব শব্দকে। কিছু কিছু শব্দ আছে, যেগুলোর গায়ে হলুদ-সবুজ-লাল-নীল -বাদামি-খয়েরি রং আছে। তোমাকে চিনতে হবে শব্দের রং। অনেক শব্দ আছে, যেগুলোর শরীর থেকে সুর বেরোয়: কোনো কোনো শব্দে বাঁশির সুর শোনা যায়, কোনো কোনো শব্দে শোনা যায় হাসির সুর। কোনো শব্দে বাজে শুকনো পাতার খসখসে আওয়াজ, কোনোটিতে বেহালার সুর। কোনো কোনো শব্দ তোমার পায়ের নূপুরের মতো বাজে। তোমাকে শুনতে হবে শব্দের সুর ও স্বর। অনেক শব্দ আছে বাংলা ভাষায় যেগুলোর শরীর থেকে সুগন্ধ বেরোয়। কোনোটির শরীর থেকে ভেসে আসে লাল গোলাপের গন্ধ, কোনোটির গা থেকে আসে কাঁঠালচাঁপার ঘ্রাণ, কোনোটি থেকে আসে বাতাবিলেবুর সুবাস। তুমি যদি দেখতে পাও শব্দের শরীরের রং, শুনতে পাও শব্দের সুর, টের পাও শব্দের সুগন্ধ, তাহলেই পারবে তুমি কবি হতে।
কবিরা শব্দ দিয়ে লেখেন নানান রকমের কবিতা। কখনো তাঁরা খুব হাসির কথা বলেন, কখনো বলেন কান্নার কথা। কখনো তাঁরা বলেন স্বপ্নের কথা, কখনো তাঁরা চারপাশে যা দেখেন, তার কথা বলেন। কিন্তু সব সময়ই তাঁরা কথা বলেন শব্দে। শব্দ বসিয়ে বসিয়ে তাঁরা বানান কবিতা। কবিতা লিখতে হলে প্রথমেই জানতে হবে নানান রকমের শব্দ। তারপর আসে শব্দ দিয়ে যা বলতে চাই, তার কথা। কিন্তু কীভাবে বলা যায় সেই কথা?
কবিতায় আমরা অনেক কিছু বলতে পারি। কখনো বলতে পারি ঘর-ফাটানো হাসির কথা। বলতে পারি টগবগে রাগের কথা। বলতে পারি খুব চমৎকার ভালো কথা। কখনো বাজাতে পারি নাচের শব্দ। আবার কখনো আঁকতে পারি রঙিন ছবি। কিন্তু সব সময়ই মনে রাখতে হবে, ওই কথা নতুন হতে হবে। যা একবার কেউ বলে গেছে, যে-ছবি একবার কেউ এঁকে গেছে, তা বলা যাবে না, সে-ছবি আঁকা যাবে না। আর কথা বলতে হবে, নাচতে হবে, ছবি আঁকতে হবে ছন্দে। তাই কবিতা লিখতে হলে শব্দকে জানতে হবে, জানতে হবে ছন্দ, আর থাকতে হবে স্বপ্ন। যার চোখে স্বপ্ন নেই, সে কবি হতে পারে না। স্বপ্ন থাকলে মনে আসে নতুন ভাবনা, নেচে নেচে আসে ছন্দ, আর শব্দ।
যে কোনো বিষয় নিয়েই তুমি লিখতে পারো কবিতা। বাড়ির পাশের গলিটা, দূরের ধানক্ষেতটা, পোষা বেড়ালটা বা পুতুলটাকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়, যদি মনে স্বপ্ন থাকে। রাস্তার দোকানিকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়, যদি স্বপ্ন থাকে। আর যা নেই, তা নিয়েও কবিতা লেখা যায়, যদি স্বপ্ন থাকে। এবার একটা কবিতা লেখা যাক। কবিতাটির নাম দিচ্ছি 'দোকানি'। রাস্তার মোড়ের দোকানদারকে তুমি-আমি চিনি। সে বিক্রি করে সাদা দুধ, খয়েরি চকোলেট, লাল পুতুল, সবুজ পান। এসব জিনিস আমরা কিনে খাই, দোকানিকে চকচকে টাকা দিই। তার জিনিসপত্র বিক্রি দেখে মাথায় আমার একটা ভাব এলো। ভাবটা হলো: আমি একটা দোকান খুলেছি দুদিন ধরে, কিন্তু সে-দোকানে দুধ, চকোলেট, পান বিক্রি হয় না।
বিক্রি হয় এমন সব জিনিস, যা কেউ বেচে না, যা কেউ কেনে না। শুধু স্বপ্নেই সে-সব জিনিস বেচাকেনা চলে। ভাবটা মাথায় এলো, সঙ্গে শব্দ এলো, আর ছন্দ এলো। প্রথমে লিখলাম:
দুদিন ধরে বিক্রি করছি
চকচকে খুব চাঁদের আলো
টুকটুকে লাল পাখির গান।
কথাটাই চমক দেয় সবার আগে: চকচকে চাঁদের আলো, টুকটুকে লাল পাখির গান বিক্রির ব্যাপারটা বেশ নতুন। সারা পৃথিবীতে খুঁজে এমন দোকান পাওয়া যাবে না। ছন্দটাও বেশ, দুলে দুলে আসছে। এ-তিনটি পঙ্ক্তি পড়ার সাথে সাথে শব্দ, ছন্দ, কথা মিলে এক রকম স্বপ্ন তৈরি হয় চোখে আর মনে। এরপর আরও এগিয়ে গিয়ে লিখলাম:
বিক্রি করছি চাঁপার গন্ধ
স্বপ্নে দেখা নাচের ছন্দ
গোলাপ ফুলের মুখের রূপ।
এখানে ছন্দ-মিল আরও মধুর। বিক্রির জিনিসগুলো আগের মতোই চমকপ্রদ। তবে এখানে স্বপ্ন আরও বেড়েছে, ছবিও আরও রঙিন। চাঁপার গন্ধ পাওয়া গেল এবং বেজে উঠল স্বপ্নে দেখা নাচের ছন্দের নূপুর। এ-নাচ স্বপ্ন ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না, এমন নাচ নাচতে পারে না কেউ। 'গোলাপ ফুলের মুখের রূপ' বলার সাথে সাথে গোলাপ ফুল একটি মিষ্টি মেয়ের মতো ফুটে উঠল, মেয়েটির মুখ হয়ে উঠল গোলাপ, আর গোলাপ হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ। স্বপ্ন জড়ো হলো চোখে।
কবিতাটিকে আমি আর লিখতে চাই না। ইচ্ছে হলে তোমরা লিখতে পার। কবিতা লিখতে হলেই নতুন কথা ভাবতে হবে, আর সে-কথাকে পরিয়ে দিতে হবে শব্দ ও ছন্দের রঙিন সাজপোশাক। তোমরা এখন ছোটো, এ-ছোটো থাকার সময়টা বেশ সুন্দর। বারবার আমার ছোটো সময়ের কথা মনে পড়ে। আমি দেখতে পাই, ছোট আমি দাঁড়িয়ে আছি পুকুরের পাড়ে, একটা সাদা মাছ লাফ দিয়ে আবার ঢুকে গেল পানিতে। দেখতে পাই শাপলা ফুটেছে, পানি লাল হয়ে গেছে। একটা চড়ুই উড়ে গেল, তার ঠোঁটে চিকন একটা কুটো। এসব আমাকে কবিতা লিখতে বলে।
তোমরা এখন ছোটো, এ বয়সে তোমরা খুব বেশি করে দেখে নেবে। যত পার, দেখ। দেখ, দেখ এবং দেখ। বুকের মধ্যে, মনের মধ্যে ছবি জমাও, রং জমাও, সুর জমাও। বড় হলে এ ছবি, সুর, রং তোমাদের খুব উপকার করবে। খুব ছোটো বয়সে কি কবিতা লেখা উচিত? ছোটো বয়সে উচিত কবিতা পড়া, পড়া এবং পড়া। চারদিকের ছবি দেখা, দেখা এবং দেখা। ছোট বয়সে বুকে জমানো উচিত শব্দ আর ছন্দ। তারপর একদিন, যখন বড়ো হবে, শব্দ, ছন্দ, ছবি, সুর, রং সব দল বেঁধে আসবে তোমার কাছে, বলবে আমাদের তুমি কবিতায় রূপ দাও। তুমি হয়তো একা একা ঘরে বসে শব্দ-ছন্দ-ছবি-সুর-রং মিলিয়ে বানাবে এক নতুন জিনিস, যার নাম কবিতা।
(সংক্ষেপিত)
উপমা - তুলনা। এখানে একটি মেয়ের নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।
নূপুর - পায়ে পরার অলংকার।
চমকপ্রদ - যা অবাক করে দেয়।
কাঁঠালচাঁপা - পাকা কাঁঠালের মতো গন্ধযুক্ত ফুল।
সাহিত্যের নানা রূপের মধ্যে একটি হচ্ছে কবিতা। রচনাটিতে কবিতার শিল্পরূপ ও তার বৈশিষ্ট্য অপরূপ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। কাকে বলা যায় কবিতা? লেখকের মতে, যা পড়লে মনের ভিতর স্বপ্ন জেগে ওঠে, ছবি ভেসে ওঠে, তা-ই কবিতা। শব্দের সঙ্গে শব্দ মিলিয়ে লেখা হয় কবিতা।
কেবল কবিরাই লিখতে পারেন কবিতা। কেননা কবিরাই স্বপ্ন দেখতে পারেন, তাঁরাই পারেন স্বপ্নের ছবি আঁকতে। নতুন ছবি নতুন ভাব কেবল কবিদের চেতনায় খেলা করে বলে তাঁরা লিখতে পারেন কবিতা। কবিতা লিখতে হলে শব্দের রূপ-রং-গন্ধ-বর্ণ-সুর ও ছন্দ চিনতে হয়, জানতে হয়। কবিরা চেনেন এবং জানেন শব্দের এসব মায়াবী রূপ। তাই তাঁরা লিখতে পারেন কবিতা।
অনেক বিষয় নিয়েই কবিতা লেখা যায়। তবে কবিতা লেখার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন স্বপ্ন। যিনি স্বপ্ন দেখতে জানেন না, তিনি লিখতে পারেন না কবিতা। স্বপ্ন দেখার জন্য শৈশব-কৈশোরে পড়তে হবে কবিতার পর কবিতা, দুচোখ মেলে দেখে নিতে হবে যা-কিছু চোখে পড়ে, তার সবটা। অর্থাৎ কবিতা লেখার জন্য চাই অভিজ্ঞতা। কবিতার রূপ ও তার রচনা-কৌশল বর্তমান রচনার উপজীব্য।
বাংলাদেশের বিশিষ্ট গদ্যশিল্পী, ভাষাবিজ্ঞানী, ঔপন্যাসিক ও কবি হুমায়ুন আজাদ ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে মুন্সীগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো: কাব্য- 'অলৌকিক ইস্টিমার', 'জ্বলো চিতাবাঘ', 'সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে', 'কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু'; উপন্যাস 'ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল', গল্প 'যাদুকরের মৃত্যু', - প্রবন্ধ 'লাল নীল দীপাবলি', 'কতো নদী সরোবর' ইত্যাদি।
হুমায়ুন আজাদ ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।
ক. তোমার পড়া কোনো কবিতা বা গল্প অবলম্বনে তোমার ভালো লাগা বা ভালো না-লাগাগুলো যুক্তিসহকারে লিখ।
খ. টেলিভিশন বা অন্য কোনো মিডিয়াতে তোমার দেখা কোনো নাটক নিয়ে একটি সমালোচনা লিখ।
১. কবিতা লিখতে হলে প্রথমেই কোনটি জানতে হবে?
ক. কথা
খ. কৌশল
গ. শব্দ
ঘ. ছন্দ
২. 'শুধু স্বপ্নেই সেসব জিনিস বেচা-কেনা চলে।' এ বাক্যে বেচা-কেনা শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. বিনিময় প্রথা
খ. ক্রয়-বিক্রয়
গ. দেনা-পাওনা
ঘ. আদান-প্রদান
নিচের কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
চপল পায় কেবল ধাই,
কেবল গাই পরির গান
পুলক মোর সকল গায়,
বিভোল মোর সকল প্রাণ।
৩. কবিতাংশে 'শব্দ থেকে কবিতা' প্রবন্ধের কবিতা রচনার কোন দিকটির পরিচয় পাওয়া যায়?
ক. শব্দ প্রয়োগ
গ. সাবলীল ভাষা
খ. ছন্দের ব্যবহার
ঘ. উপমার প্রয়োগ
৪. উপর্যুক্ত বিষয়টি নিচের কোন কথাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত?
ক. ছবিও আরও রঙিন
খ. দুলে দুলে আসছে
গ. খেলতে শব্দের খেলা
ঘ. যত পারো দেখ
১. মাহফুজা চমৎকার কবিতা লেখেন। জীবনে বিভিন্ন অংশের স্মৃতিকে শব্দের ভিতর সাজাতে পছন্দ তাঁর। মাহফুজার ভাইপো নির্ঝর তাঁকে খুব পছন্দ করে। কারণ তিনি তাঁর ভাইপো নির্ঝরকে প্রায়ই নানা রকম কবিতা শোনান। নির্ঝর ফুফুকে পেলেই ছড়া শোনার বায়না ধরে। একদিন নির্ঝর তাঁকে বলে "ফুফু তুমি এতো সুন্দর কবিতা কীভাবে লেখ?” মাহফুজা উত্তর দেন, "তুমি তোমার চারপাশের সুন্দর স্বপ্নময় শব্দগুলোকে বুঝে ধারণ করে রাখবে, দেখবে তুমিও একদিন চমৎকার কবিতা লিখতে পারবে।"
ক. কবিতা লেখার জন্য প্রথমেই কোনটি প্রয়োজন?
খ. 'কবিতার জন্য দরকার শব্দ রংবেরঙের শব্দ।' বুঝিয়ে লেখ।
গ. কবিতার বিষয়ে নির্ঝরের প্রশ্নের উত্তর 'শব্দ থেকে কবিতা' প্রবন্ধে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে লেখ।
ঘ. মাহফুজার উত্তর 'শব্দ থেকে কবিতা' প্রবন্ধের মূলভাবকে ধারণ করে কি?- যুক্তিসহ বিচার কর।
ডান পাটা মাটি থেকে এক বিঘত ওঠে, তার বেশি ওঠে না। কুমু তা হলে চলে কী করে?
মাসিরা মাকে বললেন- "কিচ্ছু ভাবিসনে, রোগ তো সেরেই গেছে, এখন ওকে ঝাড়া তিন মাস সোনাঝুরিতে মার কাছে রেখে দে, দেখিস কেমন চাঙ্গা হয়ে উঠবে।"
বাবাও তাই বললেন, "বাঃ, তবে আর ভাবনা কী, কুমু? তা ছাড়া ওখানে ওই লাটু বলে মজার ছেলেটা আছে, হেসে খেলে তোর দিন কেটে যাবে।"
কিন্তু পড়া? কুমু যে পড়ায় বড়ো ভালো ছিল। তা তিন মাস গেছে শুয়ে শুয়ে, তিন মাস গেছে পায়ে লোহার ফ্রেম বেঁধে হাঁটতে শিখে। আরও তিন মাস যদি যায় দিদিমার বাড়িতে, তবে পড়া সব ভুলে যাবে না?
মা বললেন, "পড়ার জন্য অত ভাবনা কীসের? লাটুর বাড়ির মাস্টার তোমাকেও পড়াবেন।"
মাসিরা বললেন, "বেঁচে উঠেছিস এই যথেষ্ট, তা না হয় একটা বছর ক্ষতিই হলো, তাতে কী এমন অসুবিধেটা হবে শুনি?"
হাসি, রত্না সবাই ওপরের ক্লাসে উঠে যাবে, কুমু পড়ে থাকবে, ভাবলেও কান্না পায়। কুমুর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।
সোনাঝুরিতে দিম্মার বাড়ির দোতলার বড়ো ঘরে, মস্ত জানালার ধারে আরামচেয়ারে বসে বসে চেয়ে দেখে দূরে একটা বিল, সেখানে হাজার হাজার বৃষ্টির জলের ফোঁটা পড়ছে আর অমনি বিলের জলে মিশে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে পাটা আবার একটু তুলতে চেষ্টা করে কুমু।
সন্ধে হয়ে আসছে, বৃষ্টি থেমে গেছে, বিলের জল সাদা চকচক করছে।
আকাশ থেকে হঠাৎ ছায়ার মতো কী বিলের ওপর নেমে এল। কুমু দেখে ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা ফিকে ছাই রঙের বুনো হাঁস ঝুপঝাপ করে জলে নামছে।
এক ছড়া কী যেন সাদা ফুল হাতে নিয়ে লাটু এসে বলল, "ওই দেখ, বুনোহাঁসরা আবার এসেছে।
শিকারিদের কী মজা! ইস, আমার যদি একটা এয়ারগান থাকত।"
কুমু বলল, "বন্দুক নেই ভালোই হয়েছে। অমন সুন্দর পাখিও মারতে ইচ্ছে করে!"
দিম্মাও তখন ঘরে এসে বললেন, "হ্যাঁ, ওদের ওই এক চিন্তা!"
কুমু বলল, "কোথেকে এসেছে ওরা?"
"যেই শীত পড়ে অমনি উত্তরের ঠান্ডা দেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে, বাঁধের কাছে দু-তিন দিন বিশ্রাম করে, তারপর আবার দক্ষিণ দিকে উড়ে যায়, শোনা যায় নাকি সমুদ্রের ওপর দিয়ে আন্দামান অবধি উড়ে যায় কেউ কেউ।”
লাটু কাছে এসে ফুলটা কুমুর খাটে রেখে বলল-"আবার শীতের শেষে ঝাঁকে ঝাঁকে সব ফিরে আসে, সেকথা তো বললে না ঠাকুরমা?"
লাটুর কথার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দূরে দুম দুম করে বন্দুকের গুলির শব্দ হলো, আর বুনোহাঁসের ঝাঁক জল ছেড়ে আকাশে উড়ে খুব খানিকটা ডাকাডাকি করে আবার জলে নামল।
পরদিন সকালে জানালা খুলে, পর্দা টেনে দিম্মা চলে গেলে, কুমু জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে লেবু গাছের পাতার আড়ালে, ডাল ঘেঁষে কোনোমতে আঁকড়ে-পাকড়ে বসে রয়েছে ছোট একটা ছাই রঙের বুনোহাঁস। সরু লম্বা কালো ঠোঁট দুটো একটু হাঁ করে রয়েছে, পা দুটো একসঙ্গে জড়ো করা, বুকের রঙটা প্রায় সাদা, চোখ দুটো একেবারে কুমুর চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে, কালো মখমলের মতো দুটো চোখ। একদিকের ডানা একটু ঝুলে রয়েছে, খানিকটা রক্ত জমে রয়েছে, সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে।
পাখিটাকে দেখে কুমুর গলার ভেতরে টনটন করতে থাকে; হাত বাড়িয়ে বলে, "তোমার কোনো ভয় নেই, কোনো ভয় নেই।" পাখিটা চোখ বন্ধ করে, আবার খোলে। আর একটু ডাল ঘেঁষে বসে।
লাটু কুমুর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে পাখিটাকে দেখতে পায়। "ইস! ডানায় গুলি লেগেছে বেচারার। চুন হলুদ দিয়ে বেঁধে দিলে সেরেও যেতে পারে। বলিস তো ধরে আনি।"
কুমু বলল, "কিন্তু দিম্মা কী বলবেন?"
"কী আবার বলবেন? বলবেন ছি, ছি, ছি, নোংরা জিনিস ফেলে দে, ওসব কি বাঁচে!"
কুমু জোর গলায় বলল, "নিশ্চয় বাঁচে, চুন হলুদ দিয়ে ডানা বেঁধে, গরম জায়গায় রাখলে নিশ্চয় বাঁচে।"
লাটু বলল, "কোন গরম জায়গায়?"
"কেন আমার বিছানায়, লেপের মধ্যে।"
"দেখিস, কেউ যেন টের না পায়।"
"কী করে টের পাবে, আমার বিছানা তো আমি নিজে করি। ডাক্তার আমাকে হাত-পা চালাতে বলেছে যে। আচ্ছা, ধরতে গেলে উড়ে পালাবে না তো?"
"তোর যেমন বুদ্ধি। এক ডানায় ওড়া যায় নাকি?"
"কী খাবে ও লাটু?"
লাটু ভেবে পায় না খাটের মধ্যে বিছানার ভিতরে কী খাওয়াবে ওকে। না খেয়ে যদি মরে যায়!
"এক কাজ করলে হয় না রে কুমু? ঝুড়ি দিয়ে, লেবু গাছের ডালে ওর জন্য একটা বাসা বেঁধে দিই, তা হলে ভাঙা ডানা নিয়ে আর পড়ে যাবে না, নিজেই পোকামাকড় ধরে খাবে।"

নিমেষের মধ্যে ঝুড়ি নিয়ে লাটু জানালা গলে একেবারে লেবু গাছের ডালে। ভয়ের চোটে পাখিটা পড়ে যায় আর কী! লাটু তাকে খপ করে ধরে ফেলে, কিন্তু কী তার ডানা ঝটপটানি, ঠুকরে ঠুকরে লাটুর হাত থেকে রক্ত বের করে দিল। লাটু দড়ি দিয়ে শক্ত করে ঝুড়ি বেঁধে পাখিটাকে আস্তে আস্তে তার মধ্যে বসিয়ে দিল। অমনি পাখিটা আধমরার মতো চোখ বুঁজে ভালো ডানাটার মধ্যে ঠোঁট গুঁজে দিল।
লাটু সে জায়গাটাতে নিজের পা কাটার সময়কার হলদে মলম লাগিয়ে দিয়ে আবার জানালা গলে ঘরে এল। বলল, "ঠাকুরমার কাছে যেন আবার বলিস না। বলবেন হয়তো, ছুঁস না ওটাকে।"
কুমু হাঁটতে পারে না ভালো করে, পাখিটাও উড়তে পারে না। পারলে নিশ্চয় ওই দূরে বিলে ওর বন্ধুদের কাছে চলে যেত। গাছের ডালে ঝুড়িতে ডানায় মুখ গুঁজে চুপ করে পড়ে থাকত না। কুমুর পা ভালো হলে কুমুও এখানে থাকত না। মার কাছে থাকত, রোজ ইস্কুলে যেত, সন্ধেবেলায় সাঁতার শিখত, দৌড় খেলার জন্য রোজ অভ্যাস করত। আর কোনোদিনও হয়তো কুমু দৌড়াতে পারবে না। কিছুতেই আর পায়ে জোর পায় না, মাটি থেকে ওই এক বিঘতের বেশি তুলতে পারে না। মনে হয় অন্য পাটার চেয়ে একটা একটু ছোটো হয়ে গেছে।
আর একবার জানালার কাছে গিয়ে পাখিটাকে দেখে ভালো করে, ও ডানাটাকে যে নাড়া যায় না সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। পাখিটা ঝুড়িতে বসে আস্তে আস্তে কালো ঠোঁট দিয়ে বুকের পালক পরিষ্কার করছে। তারপর কিছুক্ষণ ঠোঁটে ভর দিয়ে চুপ করে চোখ বুঁজে পড়ে থাকল; তারপর আবার চোখ খুলে গাছের ডাল থেকে কী একটা খুঁটে খেল।
কুমু বালিশের তলা থেকে ছোট্ট বিস্কুটের বাক্স থেকে একটুখানি বিস্কুট ছুড়ে দিল। পাখিটাও অমনি যেন পাথর হয়ে জমে গেল। বিস্কুটের দিকে ফিরেও চাইল না। কুমু আবার খাটে এসে বসল, নতুন গল্পের বইটা পড়তে চেষ্টা করল। পনেরো মিনিট বাদে আর একবার জানালা দিয়ে উঁকি মারল। বুকের পালক পরিষ্কার করতে করতে পাখিটা আবার কী একটা খুঁটে খেল।
গাছের ডালে পাখিটা একটু নড়ছে, একটু শব্দ হচ্ছে, কুমু ভয়ে কাঠ, এই বুঝি দিম্মা দেখতে পেয়ে মঙ্গলকে বলেন, “ফেলে দে ওটাকে, বড়ো নোংরা, ঝুড়ি খুলে আন, ওটা কে বেঁধেছে ওখানে?”
কুমু জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে পাখিটা ঘুমিয়ে আছে। কুমুও বই নিয়ে বিছানায় গিয়ে শুল। হঠাৎ জানালার বাইরে শোরগোল। চমকে উঠে দেখে একটা হলদে বেড়াল গাছের ডালে গিয়ে উঠছে। কুমু ভয়ে কাঠ; এই বুঝি বেড়াল পাখিটা খেল। কিন্তু খাবে কী, অত বড়ো পাখি তার তেজ কত! দিলো ঠুকরে ঠেলে ভাগিয়ে। দুটো কাক দূর থেকে মজা দেখল, কাছে ঘেঁষতে সাহস পেল না।
কুমু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এ মাথা থেকে ও মাথা হেঁটে বেড়াতে লাগল, খোঁড়া তো হয়েছে কী, এইরকম করে হাঁটলেই না পায়ের জোর বাড়বে। দু-বার হেঁটে কুমু এসে যখন খাটে বসল, পা দুটোতে ব্যথা ধরে গেছে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন ডান পাটা এক বিঘতের চেয়ে একটু বেশিই তোলা যাচ্ছে।
এমনি করে দিন যায়, বুনো হাঁসের ডানা আস্তে আস্তে সারতে থাকে। দু-দিন পরে পাখির ঝাঁক বিল থেকে দক্ষিণ দিকে উড়ে গেল। গাছের ডালে বসে পাখিটা একটা ডানা ঝাপটাতে লাগল। উড়বার জন্য কী যে তার চেষ্টা! কিন্তু ভাঙা ডানা ভর সইবে কেন, হাঁসটা ঝুড়ি থেকে পিছলে পড়ে নিচের ডালের ফাঁকে আটকে থাকল। লাটু তখনও স্কুল থেকে ফেরেনি, কুমু করে কী! জানালার ধারে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকল, পাখিটা অনেকক্ষণ অসাড় হয়ে ঝুলে থাকার পর আঁচড়ে-পাঁচড়ে নিজেই সেই ডালটার উপর চড়ে বসল। লাটু ফিরে এসে আবার ওকে তুলে ঝুড়িতে বসিয়ে দিল। ঠোকরালও একটু সে, তবে তেমন কিছু নয়, ডানায় আবার ওষুধ লাগিয়ে দিল লাটু।
এমনি করে দিন যায়, রোজ পাখিটা একটু করে সেরে ওঠে, ঝুড়ি থেকে ডালে নামে। আর আনন্দের চোটে কুমুও ঘরময় হেঁটে বেড়ায়, নিজের বিছানা নিজে পাতে, নিজে স্নান করে, জামা কাচে। দুপুরবেলা এক ঘুম দিয়ে উঠে নিজে বসে অঙ্ক কষে। বাড়িতে চিঠি লেখে, "মা-বাবা, তোমরা ভেবো না, আমি রোজ রোজ সেরে উঠছি, রত্নাদের বলো আমি পরীক্ষা দেব।"
এমনি করে এক মাস কাটল। তার মধ্যে একদিন খুব বৃষ্টি হয়েছিল। পাখিটা ঝুড়ির তলার গাছের ডালের আড়ালে গিয়ে লুকাল। তারপর বৃষ্টি থেমে আবার যখন রোদ উঠল, পাখিটা দিব্যি ডানা মেলে পালক শুকোল। কুমু অবাক হয়ে দেখল ডানা সেরে গেছে।
তার দু-দিন পরে দুপুরে মাথার অনেক ওপর দিয়ে মস্ত এক ঝাঁক বুনো হাঁস তীরের মতো নকশা করে উড়ে গেল। কুমুর পাখিও হঠাৎ কী মনে করে ডাল ছেড়ে অনেকখানি উঁচুতে উড়ে গেল, কিন্তু তখুনি আবার নেমে এসে মগডালে বসল। হাঁসরাও নামল। পাখিটা সেই দিকেই চেয়ে থাকল।

সারারাত বুনোহাঁসরা বিশ্রাম করে পরদিন সকালে যখন দল বেঁধে আকাশে উড়ল, কুমুর পাখিও তাদের সঙ্গ নিল। দল থেকে অনেকটা পেছিয়ে থাকল বটে, কিন্তু ক্রমাগত যেরকম উড়তে লাগল, কুমু লাটুর মনে কোনো সন্দেহ রইল না, এখুনি ওদের ধরে ফেলবে।
সে বিকেলে কুমু নিজে হেঁটে নিচে নামল, ডান পা-টা যেন একটু ছোটোই মনে হলো।
কুমু বলল, "দিম্মা, পাটা একটু ছোটো হলেও কিছু হবে না, আমি বেশ ভালো চলতে পারি। বুনো হাঁসটারও একটা ডানা একটু ছোটো হয়ে গেছে।"
শুনে দিম্মা তো অবাক! তখন লাটু আর কুমু দুজনে মিলে দিম্মাকে পাখির গল্প বলল। দিম্মা কুমুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, “ওমা, বলিসনি কেন, আমিও যে পাখি ভালোবাসি।”
দিম্মা - এখানে দিদিমাকে 'দিম্মা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।
এক ছড়া - এক গুচ্ছ।
আন্দামান - ভারত মহাসাগরে অবস্থিত ভারতের একটি দ্বীপাঞ্চল। সমুদ্রবেষ্টিত এ অঞ্চল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত।
অবধি - পর্যন্ত।
একদৃষ্টে - এক দৃষ্টিতে, অর্থাৎ চোখের পলক না ফেলে।
নিমেষ - মুহূর্ত।
বিঘত - আধা হাত পরিমাণ।
শোরগোল - চিৎকার, চেঁচামেচি।
আঁচড়ে-পাঁচড়ে - অনেক চেষ্টা করে।
মগডাল - উপরের ডাল।
'পাখি' গল্পটি লীলা মজুমদারের 'চিরকালের সেরা' গল্প-সংকলন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। গল্পের কিশোরী কুমু অসুস্থ হলে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে পরিবার। সহপাঠীরা সবাই উপরের ক্লাসে উঠে যাবে, কুমু নিচের ক্লাসে পড়ে থাকবে এই নিয়ে কুমুর ভাবনার শেষ নেই। দ্রুত সুস্থতার জন্য কুমু সোনাঝুরিতে দিদিমার দোতলা বাড়ির উন্মুক্ত পরিবেশে এলে একটি অভূতপূর্ব ঘটনার সম্মুখীন হয়।
শিকারির বন্দুকের গুলির আঘাতে একটি বুনোহাঁস আহত হলে কুমু তার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। পাখিটিকে সুস্থ করে তোলার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সমবয়সী কিশোর লাটুর সহযোগিতা নিয়ে কুমু পাখিটাকে সকল বিপদ থেকে বাঁচতে এবং দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করে। গল্পটির একটি অসাধারণ দিক হচ্ছে পাখিটির সেরে ওঠার প্রতিটি ধাপ থেকে কুমু নিজেও সুস্থ হবার প্রেরণা পায়। পাখিটির প্রতি দুজন কিশোর-কিশোরীর অকৃত্রিম মমত্ববোধ ও সমবেদনা গল্পটিকে এক অনন্য মাত্রায় উন্নীত করেছে।
লীলা মজুমদার ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার বিখ্যাত রায় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আদি পৈতৃক নিবাস বৃহত্তর ময়মনসিংহে। তিনি শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ভাইঝি। শিশু-কিশোরদের জন্য লিখেছেন গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ। তাঁর লেখা বিখ্যাত কিছু বই: 'হলদে পাখির পালক', 'দিনদুপুরে', 'বদ্যিনাথের বড়ি' 'গুপির গুপ্তখাতা'। আকাশ-ছোঁয়া কল্পনা, নির্মল হাস্য-কৌতুক এবং গল্প বলার ঢঙের কারণে শিশু-কিশোর সাহিত্যে তিনি এক ঈর্ষণীয় আসন তৈরি করেছেন। ২০০৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
ক. তোমার পছন্দের প্রাণীসমূহের তালিকা কর।
খ. বিভিন্ন সময় মানুষেরা কোন কোন প্রাণীর প্রতি কী ধরনের বিরূপ আচরণ করে থাকে?
গ. প্রাণীদের প্রতি উপযুক্ত মমত্ববোধ দেখানোর জন্য আমাদের আচরণে কী কী পরিবর্তন আনা উচিত?
১. কুমুর ধারণা অনুযায়ী দিদিমা কাকে পাখিটি ফেলে দিতে বলবেন -
ক. মা
খ. মঙ্গল
গ. লাটু
ঘ. মাসিমা
২. লাটু পাখিটির ডানায় চুন-হলুদ বেঁধে দেয়। কারণ এটি -
i. ক্ষত স্থানের জন্য উপকারী
ii. পাখিটির ডানা রঙিন করবে
iii. গ্রামীণ চিকিৎসা পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. iও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
কবুতর পোষার শখ কামালের। শুরুতে এক জোড়া কবুতর সে খাঁচাতেই পুষত। বলতে গেলে একসময় এটা নেশায় দাঁড়িয়ে যায়। তাই কবুতরের আরামদায়ক বসবাসের জন্য কাঠের খোপ বানিয়ে দেওয়ালে টানিয়ে দিয়েছে কামাল। এখন তার পাঁচ জোড়া কবুতর।
৩. উদ্দীপকে 'পাখি' গল্পের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?
ক. পাখি পোষার শখ
খ. পাখির প্রতি মমত্ববোধ
গ. পাখির প্রতি সমবেদনা
ঘ. পাখির পরিচর্যার ব্যবস্থা
8. উক্ত প্রতিফলিত দিকটি 'পাখি' গল্পের কোন চরিত্রসমূহে বিদ্যমান?
i. মা-দিদিমা
ii. কুমু-লাটু
iii. লাটু-দিদিমা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii
১. সহপাঠীদের সাথে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে একটি বিড়াল ছানার করুণ ডাক শুনে থমকে দাঁড়ায় শ্রেয়সী। হঠাৎ দেখে রাস্তার পাশে একটি গর্তে একটি বিড়াল ছানা আটকে আছে। বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে শ্রেয়সী সেটিকে পরিষ্কার করে কোলে তুলে নেয়। বাড়িতে ফেরার পর শ্রেয়সীর সেবা-যত্নে বিড়াল ছানাটি যেন প্রাণ ফিরে পেল। খুব অল্প সময়ে সে তাদের পরিবারেরই একজন হয়ে উঠল। কিন্তু ওর ভাই সুজা তাকে সহ্য করতে পারত না, প্রায়ই মারধর করত। একদিন শ্রেয়সী স্কুল থেকে ফিরে বিড়াল ছানাটিকে আর খুঁজে পেল না।
ক. হাঁসরা গিয়ে কোথায় নামল?
খ. কুমু-লাটুর মনে কোনো সন্দেহ রইল না কেন?
গ. শ্রেয়সীর মাধ্যমে 'পাখি' গল্পের কোন বিশেষ দিকটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে?-ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'সুজার মানসিকতা কুমু বা লাটুর মতো হলে বিড়াল ছানাটিকে হারাতে হতো না শ্রেয়সীর।'- বিশ্লেষণ কর।
অন্তুর মামা বড়ো বেশি একটা ঢাকা শহরে আসেন না। ওর মা চিঠি লিখে কত বলেন, 'কাজল তুই ঢাকা শহরে চলে আয়। আমার বাসাতেই থাকবি যদ্দিন চাকরি না হয়।' কাজল মামা তবু আসে না। গ্রাম নাকি খুব ভালো লাগে কাজল মামার।
১৯৭১ সালে কাজল মামা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। পড়তে পড়তেই বেঁধে গেল যুদ্ধ। একদিন ঢাকা ছেড়ে হঠাৎ সে গ্রামে এসে হাজির। তারপর রাতদিন এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে ছেলেদের জোগাড় করে মিছিল মিটিং। রাইফেল জোগাড় করে ট্রেনিং। আরও কত কি! অন্তর নানা কত বকতেন, ‘বাবা, এসব করিস নে। বিপদে পড়বি।’
'বাঘা বাঙালিরা এবার যুদ্ধ করবে, বাবা। স্বাধীনতা এবার আসবেই।' সাহস নিয়ে বলত কাজল মামা।
সেই কাজল মামার যুদ্ধের গল্প শুনবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে অন্তু। বার্ষিক পরীক্ষার পর থেকেই। মা ওকে বুদ্ধি শিখিয়ে দিয়েছে, 'তুই এক কাজ কর অন্তু। চিঠি লেখ মামাকে। বল, এবারের একুশে ফেব্রুয়ারিতে যেন অবশ্যই ও ঢাকা আসে। আরও বল, তুই যুদ্ধের গল্প শুনবার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছিস। দেখবি ঠিক আসবে।'
বুদ্ধিটা অন্তুর মা'র হলেও এমন একটা কৌশল চিন্তা করত সে বেশ ক'দিন আগে থেকেই। কাউকে না জানিয়ে অন্তু চিঠি লিখেছে। সেও প্রায় দশ-বারো দিন হয়ে গেছে। আজ আঠারো তারিখ। তিন দিন বাদেই মহান একুশে ফেব্রুয়ারি। ওর কেন যেন বিশ্বাস কাজল মামা আর কারও কথা শুনুক না শুনুক তার কথা রাখবেই, আসবেই সে ঢাকা।
অন্তু বরাবর রাত ন'টা-সাড়ে ন'টায় ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আজ রাতে সে দশটারও ওপরে জেগে থাকল। মা বললেন, ‘ঘুমাতে যাস নে কেন?’
অন্তু খুলে বলে না কিছু। এগারোটা বাজতেই কিন্তু ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসে ওর। লেপের নিচে ঢুকতে ঢুকতেই সে কী গভীর ঘুম!
ভোরবেলায় সে দেখল কাজল মামা তার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। লেপ থেকে বেরিয়ে এক লাফে উঠে বসল সে বিছানায়।
মামা বললেন, 'ভালো আছিস তুই অন্তু? শেষ রাতের ট্রেনে এলাম। এসে দেখি তুই ঘুমাচ্ছিস।' অন্ত বলে, 'আজ কিন্তু উনিশ তারিখ, তা তো জানো মামা। দু'দিন বাদেই একুশে ফেব্রুয়ারি।'
মামা বললেন, ‘ঠিক আছে খানিকক্ষণ রেস্ট নিয়েই বেরুব তোকে নিয়ে। যেখানেই যেতে চাস সেখানেই যাব। পাঁচদিন আমি ঢাকায় থাকব এর মধ্যে চারদিনই তোর সাথে। যেখানে যেতে চাইবি যাব। যত গল্প শুনতে চাস শোনাব।’
মোহাম্মদপুরের নূরজাহান রোড থেকে একটি রিকশায় চাপল অন্তু আর কাজল মামা। লালমাটিয়া-ধানমণ্ডি হয়ে রিকশা চলছিল। মামা বললেন, 'এই যে রাস্তাটা দিয়ে আমরা যাচ্ছি এর নাম সাতমসজিদ রোড। জানিস?'
'কি যে বলো মামা! জানব না কেন?'
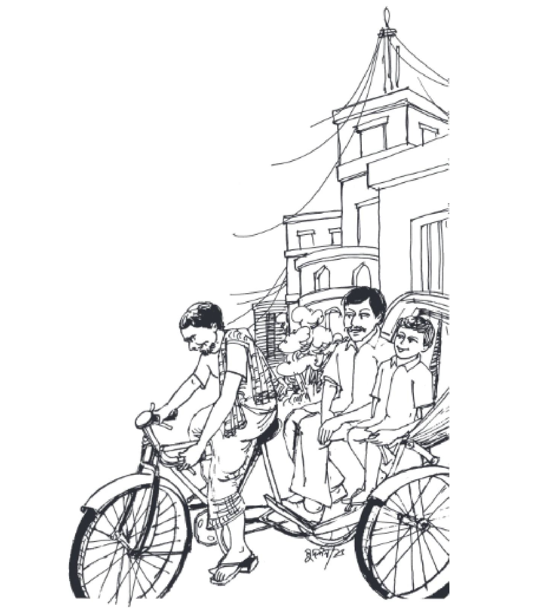
'ঠিক আছে বল দেখি, সাতমসজিদ নাম হয়েছে কেন রাস্তাটার?'
'তা তো ঠিক জানি না।'
'এই জন্যই বলছিলাম, অতীতের অনেক জিনিসই জেনে রাখা ভালো আমাদের। অতীত মানে আমাদের আগের দিন। পুরোনো দিনের ওপরেই তো বর্তমানের দিন-রাত গড়ে ওঠে।'
কাজল মামা সংক্ষেপে বললেন। এই ঢাকা শহরের আগের নাম জাহাঙ্গীরনগর। মোগল বাদশা জাহাঙ্গীরের নামে। সেই সময় থেকেই শহরের আনাচে-কানাচে অনেক মসজিদ তৈরি হতে থাকে। এই রাস্তাটা পিলখানার মোড় থেকে মোহাম্মদপুর এসে সাতগম্বুজ মসজিদে ঠেকেছে। সেই পুরোনো মসজিদের নামেই রাস্তাটার নাম হয়েছে সাতমসজিদ রোড।
রিকশাটা নিউমার্কেট পেরিয়ে নীলক্ষেত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্যে ঢুকতেই অন্তু জিজ্ঞেস করল, 'তুমি নাকি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে মামা?'
'হ্যাঁ, পড়তাম একদিন। তুই জানলি কী করে?'
'মা বলছিল তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়তে তখনই যুদ্ধে গিয়েছ।'
'অন্তু, যুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে অনেক তফাৎ। যুদ্ধ হয় রাজায় রাজায়, একদেশে আরেক দেশে, মানুষের লোভ লালসায়। যুদ্ধে শক্তি দেখায় একজন মানুষ কষ্ট হয় সাধারণ মানুষের। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ হয় স্বাধীনতার -জন্য, একটি জাতি হিসেবে বেঁচে থাকবার জন্য, সব অন্যায়-অত্যাচার আর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার জন্য।
একাত্তর সালে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম- সাধারণ যুদ্ধ নয়।'
দেখতে দেখতে রিকশাটা রোকেয়া হল আর শামসুন্নাহার হল পেরিয়ে জগন্নাথ হলের সামনে এসে পৌঁছাল। কাজল মামা বললেন, 'এই যে ডান পাশে বিল্ডিংটা দেখছিস, ওটার নাম কি জানিস?'
'না।'
'জগন্নাথ হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা থাকে।'
'তুমি থাকতে এখানে?'
'না। আমি থাকতাম হাজী মুহাম্মদ মহসীন হলে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এই হলের কয়েক শত ছাত্রকে ওই মাঠটাতে একসাথে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরেছিল।'
'কেন?'
'কারণ পাকিস্তানি সামরিক শাসকেরা আমাদের বাংলাদেশটাকে গোলাম করে রাখতে চেয়েছিল। আর ছাত্ররা যেহেতু তরুণ এবং পাকিস্তানিদের সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করত, সেহেতু ওদের গুলির শিকার হলো ওরাই প্রথম।'
কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের সামনে এসে রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিলেন কাজল মামা। দু'দিন বাদেই মহান একুশে ফেব্রুয়ারি। মামা বললেন, 'অন্তু, এই পৃথিবীতে অসংখ্য-অগণিত জাতি বা গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। ওদের মধ্যে যাঁরা স্বাধীন হয়েছেন তাঁদের সেই স্বাধীনতা লাভের পেছনে প্রচুর ত্যাগ-তিতিক্ষা আছে। অনেক রক্তের ইতিহাস আছে। হাজারো লক্ষ প্রাণদানের করুণ কাহিনি আছে। আর সেইসব রক্তের স্মৃতিকে ভবিষ্যতের বংশধরদের জন্য ধরে রাখতে গিয়েই দেশে এই শহিদ মিনারের মতো স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে।'
অন্তু মামাকে বলে, 'মামা, এবার কি তুমি ফুল দিতে আসবে শহিদ মিনারে?'
'আসব। গ্রামে থাকি, অনেক বছর আসতে পারি নি। এবার তোকে নিয়েই আসব। বলতো অন্তু, শহিদ মিনার বাঙালির স্মৃতিসৌধ কেন?'
'মায়ের ভাষা বাংলাকে রক্ষা করতে গিয়ে এখানে অনেক বাঙালি প্রাণ দিয়েছিল একদিন।'
অন্তর স্পষ্ট উত্তরে কাজল মামা খুব খুশি হলেন। বললেন, 'তুই তো বেশ কিছু জানিস অন্তু। তোর উত্তরে খুব খুশি হয়েছি আমি। এই শহিদ মিনার হলো আমাদের ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদদের স্মৃতির মিনার। পাকিস্তানের শাসকেরা আমাদের বাঙালিদের ওপর তাদের উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বাঙালিরা তা মেনে নেয় নি। তাই ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে ঠিক এই জায়গাটায় যখন তাঁরা উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিল তখনই পাকিস্তানি পুলিশ গুলি করে অনেককে হত্যা করেছে।
চাপ চাপ রক্তে এই জায়গার মাটি ভিজে গেছে। ওই রক্তের বিনিময়েই আমরা বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি।'
অন্তর মুখ দেখে কাজল মামা বুঝলেন সে মন খারাপ করেছে। মানুষ মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে এ ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না অন্ত। মামাকে বলে, 'মামা, তুমিও তখন এখানে ছিলে?'

‘নারে পাগল। আমি তো তখন তোর মতোই ছোটো। এখানে যাঁরা বাহান্ন সালে রক্ত দিয়েছেন তাঁরা সবাই আমার বড়ো। ওরা আমাদের পিতৃপুরুষ ওদের আমরা চিরদিন মনে রাখব - শ্রদ্ধা করব।’
কাজল মামার হাত ধরে অন্তু একের পর এক সিঁড়ি ডিঙিয়ে শহিদ মিনারের ওপরে ওঠে। মামার কাছে একুশে ফেব্রুয়ারির কাহিনি শুনে সে আগ্রহী হয় নিজ জাতির অতীত সংগ্রামের আরও কাহিনি শুনতে। কেউ তো আগে এমন করে বলে নি তাকে। অথচ কত কাহিনি আছে বাঙালি জাতির। অন্তু বলে, ‘তুমি আমাকে আরও কাহিনি বলো মামা।’
‘একুশে ফেব্রুয়ারির দিন যখন ফুল দিতে আসবি, সেদিন আরও বলব। আজ শুধু এটুকুই বলি- এই একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদেরা হচ্ছে আমাদের জাতির প্রথম শহিদ। ওরা রক্ত দিয়েছিল বলেই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেয়েছিল। শুধু তা-ই নয় একুশে ফেব্রুয়ারি থেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালিদের স্বাধীনতার মূল সংগ্রাম শুরু হয়। সেই সংগ্রাম আরও উনিশ বছর ধরে চলে। এই উনিশ বছরে অসংখ্য মানুষ মারা যায়, অনেক মায়ের কোল খালি হয়ে যায়। তারপর আসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ।’'সেই
মুক্তিযুদ্ধে তুমি ছিলে?'
'হ্যাঁ, আমি ছিলাম সেই মুক্তিযুদ্ধে।'
'বলতে হবে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের গল্প। বাসায় ফিরে দুপুরের খাবার খেয়েই বলবে। ঠিক তো?'
'ঠিক।'
শহিদ মিনার থেকে নেমে কাজল মামা আর অন্ত জুতো পরে নেয়। ফিরে আসার সময় মামা বলেন, 'অন্ত চল, আমরা দু'জনে এক মিনিট দাঁড়িয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদদের শ্রদ্ধা জানাই।'
অন্তু ও কাজল মামা নীরবে শ্রদ্ধা জানায়।
(সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত)
হানাদার বাহিনী - অন্যায়ভাবে আক্রমণকারী বাহিনী। এখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বোঝাচ্ছে। এই বাহিনী বাংলার নিরীহ জনগণের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে।
তিতিক্ষা - হনশীলতা।
সামরিক শাসন - সামরিক বাহিনী দ্বারা যখন রাষ্ট্রের শাসন পরিচালিত হয় তখন সেই শাসনকে সামরিক শাসন বলা হয়।
পিতৃপুরুষ - পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ প্রভৃতি পূর্বপুরুষ।
শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশ, জাতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করা।
'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পটির কিশোর অন্ত ঢাকায় বসবাস করে। মায়ের কাছে মুক্তিযোদ্ধা কাজল মামার সাহসী সংগ্রামের গল্প শুনে অন্তুর মনে মামার মুখ থেকে যুদ্ধের গল্প শোনার আগ্রহ জাগে। সে মামার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। একুশে ফেব্রুয়ারির দু'দিন আগে কাজল মামা ঢাকায় আসেন। মামার কাছেই শুরু হয় অন্তর অতীত সম্পর্কে তথ্যনির্ভর ইতিহাসের পাঠ। অন্তু জানতে পারে ঢাকা শহরের নামের ইতিহাস, সাতমসজিদ রাস্তার নামের ইতিহাস। জানতে পারে যুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের পার্থক্য। পঁচিশে মার্চের রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণ ও ছাত্রদের প্রতিবাদী ভূমিকার কথা। ঢাকা শহরে রিকশায় ঘুরতে ঘুরতে কিশোর অন্তু স্মৃতিসৌধ, মাতৃভাষা আন্দোলন, শহিদ মিনারসহ বাঙালি জাতির পিতৃপুরুষ কারা সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।
কথাসাহিত্যিক হারুন হাবীব একজন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা এবং ৭১-এর রণাঙ্গন সংবাদদাতা। তিনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে প্রচুর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা লিখেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি হলো: প্রিয়যোদ্ধা', 'ছোটগল্প-সমগ্র ১৯৭১,' 'মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত প্রবন্ধ, 'Blood and Brutality' ইত্যাদি। তাঁর জন্ম ১৯৪৮ সালে জামালপুরে।
ক. ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনে আমাদের কী কী করা উচিত ১০টি বাক্যে তা লিখ।
খ. তোমার গ্রাম/মহল্লার যেকোনো একজন মুক্তিযোদ্ধার সংক্ষিপ্ত জীবনী কমপক্ষে ১৫টি বাক্যে লিখ।
১. মোগল আমলে ঢাকার নাম ছিল?
ক. বাবরনগর
খ. হুমায়ুননগর
গ. আকবরনগর
ঘ. জাহাঙ্গীরনগর
২. অন্তর নানা কাজলকে বকতেন কেন?
ক. ভাষা আন্দোলনে যুক্ত থাকায়
খ. গ্রামে চলে যাওয়াতে
গ. মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে
ঘ. চাকরি হয়নি বলে
নিচের উদ্দীপক পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
(১) "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি"
(২) "মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রুজলে।"
৩. উদ্দীপকের প্রথম অংশটি 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পের কোন দিকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?
i. ভাষা আন্দোলন
ii. মুক্তিযুদ্ধ
iii. ইতিহাস-ঐতিহ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. i, ii ও iii
৪. উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশের মূলভাব নিচের কোন কথাটিতে প্রতিফলিত হয়েছে?
ক. স্বাধীনতা এবার আসবেই
খ. যুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে অনেক তফাৎ
গ. অনেক রক্তের ইতিহাস আছে
ঘ. ওরা আমাদের পিতৃপুরুষ
১. সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী প্রিয়তি বাবা-মায়ের সঙ্গে প্রথমবারের মতো ঢাকায় বেড়াতে এসেছে। একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাবা-মা ওকে নিয়ে যায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে। বাবা-মায়ের সাথে সেও ফুল দিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। বাবার কাছে ভাষাশহিদদের আত্মত্যাগের কথা শুনে গর্বে মনটা ভরে ওঠে প্রিয়তির।
ক. ১৯৭১ সালে কাজল মামা কোথায় পড়ত?
খ. 'যুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে অনেক তফাৎ'- উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।
গ. অন্তু ও প্রিয়তির মনোভাব কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পের সম্পূর্ণ ভাবকে ধারণ করে না।"- উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

ছবি আঁকতে ইচ্ছে হচ্ছে?
কাগজ তো সাদা। পেনসিলে আঁকা যায়। হাতের কলমটা দিয়েও আঁকা যায় এই সাদা জমিনে।
রং হলে খুউব ভালো হয়। ইচ্ছেমতো লাল, নীল, সবুজ, বেগুনি, হলুদ, কালো রং ঘষে ঘষে সাদা কাগজটা ভরে ফেলা যায়। সুন্দর এক রঙিন ছবি আঁকা হয়ে যায়।
হলুদ, নীল ও লাল এই তিনটিই কিন্তু আসল রং। এই তিন রং থাকলে নানা রঙে ভরা পরিপূর্ণ রঙিন ছবি আঁকা যায়। এই তিনটি রং মিলিয়ে মিশিয়ে অনেক রং পাওয়া যায়। যেমন-
হলুদ ও নীল মেশালে পাবে সবুজ।
নীল ও লাল মেশালে পাবে বেগুনি।
লাল ও হলুদ মেশালে পাবে কমলা।
এভাবে একটির সঙ্গে আরেকটি রং বা একাধিক রং মিশিয়ে কত রকম রং যে পাওয়া যায় তার মধ্যে কয়েকটি রং ছাড়া সবগুলো সঠিক নামে চেনা সম্ভব নয়। তাই সিদ্ধান্ত হয়েছে লাল, হলুদ ও নীল এই তিনটিই হলো মৌলিক রং বা প্রাথমিক রং। সবুজ, কমলা ও বেগুনি হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের বা মাধ্যমিক রং এবং অন্যান্য রং পরবর্তী পর্যায়ের। সাদা ও কালো রং ছবি আঁকার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মৌলিক রং মিলিয়ে মিশিয়ে এই দুটো রং পাওয়া যাবে না। তবে সবুজ ও লাল ঘন করে মিশিয়ে কালোর কাছাকাছি গাঢ় একটি রং তৈরি করা সম্ভব।
রংধনুর সাতটি রং। বৃষ্টির পর আকাশে যখন রংধনু ফুটে ওঠে, একটি একটি করে গুণে সাতটি রং খুঁজে বের করা যায়। হলুদ, কমলা, লাল, সবুজ, নীল, বেগুনি ও গোলাপি।
বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। বছরের ১২ মাসকে আমরা ২ মাস করে প্রকৃতি ও আবহাওয়ার কারণে ভাগ করে নিয়েছি।
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এই ২ মাস গ্রীষ্মকাল। আবহাওয়া থাকে শুষ্ক ও গরম। বৃষ্টি হয় কম। গাছপালা, খাল-বিল-নদী শুকিয়ে যায়। প্রচণ্ড রোদে গাছের সবুজ-সতেজ রং বিবর্ণ হয়ে যায়। আবার হঠাৎ করে আকাশে কালো রঙের মেঘের ছুটাছুটি, বিদ্যুৎ চমকানো, সঙ্গে কানে তালালাগা প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হয়। তারপর ঝড় ও বৃষ্টি। প্রকৃতিতে রঙের নানা রকম খেলা চলে। রং-বেরঙের ফল আম, জাম, কলা, লিচু, তরমুজ এই গ্রীষ্ম ঋতুতে পাওয়া যায়। লাল, নীল, কালো, হলুদ, গোলাপি, কমলা সবুজ রঙের এই বাহারি ফলগুলোর স্বাদও মিষ্টি।
বর্ষাকাল হলো আষাঢ়-শ্রাবণ মাস। ঝিরঝিরে অল্প বৃষ্টি থেকে ঝর ঝর করে প্রবল বেগে বৃষ্টি হয় এ সময়। মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, ঝিল-বিল পানিতে টইটুম্বুর। পানি পেয়ে গাছপালা সতেজ হয়ে যায়- নানা রকম সবুজ রঙে ভরে যায় গাছপালা, বন-জঙ্গল, ধানক্ষেত, পাটক্ষেত ইত্যাদি। সাদা ও কমলা রঙের কদম ফুল বর্ষা ঋতুর ফুল। এই ঋতুতে সতেজ ও সবুজ কচুবনে যখন কমলা রঙের লম্বা লম্বা ফুল ফোটে, চমৎকার লাগে দেখতে। কচুফুল তরকারি হিসেবেও সুস্বাদু।
শরৎকাল- সাদা ও স্বচ্ছ নীলের ছড়াছড়ি। ভাদ্র ও আশ্বিন এই দুই মাস শরৎকাল। এ সময়ে বৃষ্টি বসে যায়। সুন্দর নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো গুচ্ছ গুচ্ছ মেঘ ভেসে বেড়ায়। গাছপালা নদীনালা প্রকৃতির সবকিছু এই ঋতুতে ঝকঝকে। নদীর ধারে ও বিলে অল্প পানিতে কাদামাটিতে সবুজ গাছ থেকে বের হয়ে আসে নরম সাদা কাশফুল। বাতাসের দোলায় এই কাশফুল যখন দোলে, সুন্দর নরম রঙের কারণে মন তখন আনন্দে নেচে ওঠে। বিলে, পুকুরে এ সময় শাপলাফুল ফোটে। বেশির ভাগ শাপলা সাদা, লাল শাপলাও আছে যা দেখতে খুবই সুন্দর। ভরা নদী ও খালে সাদা, লাল, নীল ও হলুদ বিভিন্ন রঙের পালতোলা নৌকা-চলাচলের দৃশ্য মোহনীয়।
হেমন্ত ঋতু হলো কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস। সবুজ ধানক্ষেতের রং হলুদ হতে শুরু করে। ঋতুর শেষ দিকে - অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে পুরো মাঠে হলুদ বা গেরুয়া রঙের বাহার। ধান পেকে গেছে। চাষিরা দল বেঁধে ফসল কাটা শুরু করে।
এরপরেই পৌষ ও মাঘ মাস- - শীতকাল। বনে-জঙ্গলে, বাড়ির আঙিনায় সর্বত্রই নানা রঙের ফুল ফোটা শুরু হয়। এই ফুল ফোটা শীতের পরে বসন্ত ঋতু পর্যন্ত চলতে থাকে। শিমুল, পলাশ আর কৃষ্ণচূড়া গাছে যখন ফুল ফোটে, হলদে গাছের ঝলমলে হলুদ রঙের ফুলে পুরো প্রকৃতি যেন রঙের উৎসবে মেতে ওঠে। মাঠে তিলের ক্ষেতে সাদা ও হালকা বেগুনি ফুল এবং সরষের ক্ষেতে ফুলে ফুলে হলুদের বন্যা নামে এই শীতকালেই। শীতের কারণে মানুষের পোশাকে আসে রঙের বৈচিত্র্য। লাল, নীল, হলুদ, কালো বিচিত্র রঙের গরম কাপড় ও টুপি ব্যবহার করে মানুষ।
শীতকালে কুয়াশাও প্রকৃতিতে ধোঁয়াটে ধরনের এক মায়াবী রং আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। খুবই ঠান্ডা ও বরফ-পড়া দেশ থেকে চলে আসে আমাদের দেশে লক্ষ পাখি। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে এরা আশ্রয় নেয় আমাদের দেশের খালে-বিলে-নদীতে যাদের বলা হয় অতিথি পাখি। রং-বেরঙের পালক এসব পাখির। শীতের শেষে বসন্তের শুরুতে এরা আবার চলে যায় নিজের দেশে।
ফাল্গুন ও চৈত্র বসন্তকাল। ষড়ঋতুর শেষ ঋতু। এ সময় গাছে গাছে যেন প্রতিযোগিতা- কে কত সুন্দর ও সতেজ ফুল ফোটাতে পারে। নানা রঙের পালকে সেজে ছোটবড় সব পাখি গাছে গাছে নেচে বেড়ায়, উড়ে বেড়ায়। ফুলের মধু খেয়ে উড়ে বেড়ায় আনন্দে। অন্যদিকে হাজার লক্ষ রঙিন প্রজাপতি। এত রং-বেরঙের যে হিসেব করা সম্ভব নয়। নানা রঙের মোহময় প্রেরণায় মানুষও স্বভাবসুলভ আনন্দে মেতে ওঠে। বাসন্তী ও উজ্জ্বল রঙের পোশাকে, সাজসজ্জায় উৎসবে মেতে ওঠে। তাই বসন্ত ঋতুই হলো রঙের ঋতু।
অনেক কাল আগে থেকেই বাংলাদেশের ষড়ঋতুতে আমাদের পরিবেশে, নিসর্গে উজ্জ্বল-সুন্দর নানা রঙের যে সমাবেশ ঘটেছে রূপের রকমফের ঘটে চলেছে তা বাঙালির মনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। তাই আমরা দেখি আমাদের গ্রামীণ সমাজের লোকশিল্পীরা মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল, কাপড় ও তুলার পুতুল, সোনার পুতুল, লক্ষ্মীসরা, শখের হাঁড়ি, নকশিকাঁথা, হাতপাখা, পাটি, গল্প বলার পটে তথা লোকশিল্পে উজ্জ্বল ও সতেজ রং ব্যবহার করে ছবি ও শিল্পকে সুন্দর ও মোহনীয় রূপ দিয়ে চলেছে তাঁতে তৈরি কাপড়ে তাঁতিরা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকেরা তাদের তৈরি তাঁতের পোশাকে রঙিন সুতোর বুনটে নানা রঙের ঝলমলে মনকাড়া সব শাড়ি ও পোশাক বানিয়ে চলেছে। আমাদের শিশুরা এখন ছবি আঁকে। বিভিন্ন দেশের তুলনায় বাংলাদেশের শিশুদের ছবির রং অনেক উজ্জ্বল, সাহসী এবং মৌলিক রং ঘেঁষা। তাই খুব সহজেই বাংলার শিশুদের ছবিকে আলাদা বৈশিষ্ট্যে চেনা যায়।
চারুকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত চিত্রশিল্পীদের ছবির সামনে দাঁড়ালে একই কথা মনে হবে। বাংলাদেশের শিল্পীরা অনেক মুক্ত, সহজ ও সাহসী। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, বেগুনি, কমলা, কালো ও সাদা রংকে শিল্পীরা সুন্দরভাবে ছবিতে, নকশিকাঁথায়, হাতপাখায়, পুতুলে, হাঁড়িপাতিলে ব্যবহার করছেন। তাই বাংলার শিল্পীদের শিল্পকর্ম সারা বিশ্বে প্রশংসা পাচ্ছে।
খুউব - খুব। জোর দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে খুউব।
মৌলিক রং - যার মধ্যে অন্য কোনো রঙের মিশ্রণ ঘটেনি। একটি মাত্র রঙে গঠিত।
ষড় - ছয়।
প্রচণ্ড - কড়া, কঠোর।
গেরুয়া - মাটির মতো রং।
বাহার - শোভা, সৌন্দর্য।
সর্বত্র - সব জায়গায়।
ঋতুভেদে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করে তোলা।
আমরা চারপাশে গাছ-লতাপাতা, ফুল, মাঠ, নদী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি দেখি। তাদের রূপ আছে। রং আছে। সেই রূপকে নানান রঙে নিজের মতো যাঁরা আঁকেন তাঁদের আমরা বলি চিত্রশিল্পী। বিভিন্ন ঋতুতে আমাদের চারপাশের পরিবেশের রূপ ও রং বদলে যায়। চিত্রশিল্পীরাও তাঁদের ছবিতে রঙে-রেখায় ফুটিয়ে তোলেন। ছবির সেই নানান রং ও রঙের বৈচিত্র্যের কথাই লেখক হাশেম খান তাঁর 'ছবির রং' লেখাটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন।
শিল্পী হাশেম খান ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চিত্রকলা বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর ও ঢাকা নগর জাদুঘরের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ছবি আঁকার পাশাপাশি তিনি সাহিত্যচর্চাও করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই: 'ছবি আঁকা ছবি লেখা', 'জয়নুল গল্প', 'গুলিবিদ্ধ ৭১'।
ক. প্রকৃতিনির্ভর ছড়া, কবিতা বা গল্প লিখে দেয়াল-পত্রিকা প্রকাশ (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর দলগত কাজ)।
খ. প্রকৃতিনির্ভর ছবি এঁকে প্রদর্শনীর আয়োজন (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর দলগত কাজ)।
গ. শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে নিয়ে সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন।
১. ছবি আঁকার মৌলিক রংগুলো কী?
ক. হলুদ, সবুজ ও বেগুনি
খ. লাল, হলুদ ও কমলা
গ. লাল, নীল ও হলুদ
ঘ. হলুদ, নীল ও সবুজ
২. মাঠে গেরুয়া বাহার দেখে বোঝা যায়-
i. অগ্রহায়ণ মাস চলছে
ii. মাঠে ধান পেকেছে
iii. মানুষের পোশাকে বৈচিত্র্য এসেছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. iও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বড়ো বোনের সাথে বেড়াতে যায় সবিতা। সেখানে তার বোন তাকে বিশ্ববিদ্যালয়
ক্যাম্পাস ঘুরে ঘুরে দেখায়। হঠাৎ সবিতার চোখ ক্যাম্পাস-সংলগ্ন বিলে আটকে যায়। সেখানে রংবেরঙের
হাজার হাজার পাখির মেলা বসেছে। কিন্তু কোনো পাখিই তার পরিচিত নয়।
৩. উদ্দীপকের অচেনা পাখিগুলো ছবির রং রচনায় উল্লেখিত কোন ঋতুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়?
ক. বর্ষাকাল
খ. শরৎকাল
গ. শীতকাল
ঘ. বসন্তকাল
8. উদ্দীপকে উল্লেখিত পাখিগুলোকে আমাদের দেশে কী বলে?
ক. মায়াবী পাখি
খ. রংবেরঙের পাখি
গ. বসন্তের পাখি
ঘ. অতিথি পাখি
১. গত ডিসেম্বরে রিংকু তার মামার বাড়ি আলোকদিয়ায় বেড়াতে যায়। তার মা তাকে সেখানকার বিদ্যালয়ে নিয়ে যান। বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে নানা রঙের অনেক ফুল আর প্রজাপতি দেখে সে মুগ্ধ হয়। সেখানে সে শিক্ষার্থীদের তৈরি উজ্জ্বল রঙের নানা ধরনের পুতুল, বিভিন্ন রং দিয়ে আঁকা ছবি দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে।
ক. চাষিরা কোন মাসে দল বেঁধে ফসল কাটে?
খ. 'এই তিনটি রং মিলিয়ে মিশিয়ে অনেক রং পাওয়া যায়।'- ব্যাখ্যা কর।
গ. বিদ্যালয়ের দৃশ্যে 'ছবির রং' প্রবন্ধের কোন ঋতুর পরিচয় পাওয়া যায়?- ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "উদ্দীপকটি 'ছবির রং' প্রবন্ধের আংশিক ভাব প্রকাশ করছে।"- বিশ্লেষণ কর।

(গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছে সোমেন, সাবু ও আরজু। সবাই গান গাইতে গাইতে স্কুলে যাচ্ছে। বেশ তাড়া তাদের। একসময় হঠাৎ থেমে যায় আরজু। ওরা আরজুকে ফেলেই চলে যায়। আরজুর ব্যথা পায়ে। সাবু ফিরে আসে।)
সাবু - কী হলো আবার?
আরজু - আমি যে আর হাঁটতে পারছি না।
সাবু - রোজ রোজ তোর জন্য আমি স্যারের বকুনি খেতে পারব না।
আরজু - ঠিক আছে তোরা যা, আমি একাই এক্ষুনি যাব।
সাবু - থাক তাহলে।
(চলে যায় সাবু। আরজু বসে পড়ে। এ সময়ই ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক আইসক্রিমওয়ালা।)
আইসক্রিমওয়ালা - আইসক্রিম, আইসক্রিম চাই আইসক্রিম। কী হলো আরজু মিয়া, তুমি এখানে বসে কী করছ?
আরজু - কিছু না।
আইসক্রিমওয়ালা - স্কুলে যাবে না?
আরজু - না।
আইসক্রিমওয়ালা - স্কুলে ফাঁকি দেওয়া কিন্তু খুব খারাপ, আমিও খুব স্কুল ফাঁকি দিতাম। আমার অবস্থা দ্যাখো। যদি লেখাপড়াটা করতাম তাহলে কি আর আইসক্রিম ফেরি করতে হতো? যাও স্কুলে যাও। চাই আইসক্রিম, আইসক্রিম।
আরজু - ভাই শোনো- তুমি কোন দিকে যাচ্ছ?
আইসক্রিমওয়ালা - আমি তো যাব ঐ বাজারের দিকে।
আরজু - আজ স্কুলের দিকে যাবে না? আইসক্রিম খাব, টিফিন পিরিয়ডের সময়।
আইসক্রিমওয়ালা - ক্লাস যখন চলে তখন তো আর আইসক্রিম বিক্রি হয় না। আমার বাজারের সময় চলে যায়। চাই আইসক্রিম। (আইসক্রিমওয়ালা চলে যায়। হাওয়াই মিঠাইওয়ালার প্রবেশ।)
আরজু - ভাই শোনো।
হাওয়াই মিঠাইওয়ালা - শুধু শুধু ডাকছ কেন? এভাবে সময় নষ্ট হলে আমার হাওয়াই মিঠাই যে শূন্যে মিলিয়ে যাবে।
আরজু - তোমার হাওয়াই মিঠাই কি মেঘের মতো যে, মেঘ জমছে আর শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।
হাওয়াই মিঠাওয়ালা -হ্যাঁ, মেঘের চাইতেও অনেক হালকা তাই তো মিলিয়ে যায়। যাই চাই হাওয়াই মিঠাই (চলে যায়)।
আরজু -এখন আমি কী করব? বাড়ি গেলে বাবা বলবে স্কুলে ফাঁকি দেওয়ার মতলব-স্কুলে গেলে স্যার বলবে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। এখন কী হবে?
(টিফিনের ঘণ্টা বাজে। সোমেন, সাবু ও আরও ছেলেমেয়ে টিফিন পিরিয়ডে বেরিয়ে আসছে। তারা খেলছে। এ সময়ে আসেন লতিফ স্যার।)
লতিফ স্যার -এই সাবু, এদিকে শোনো- আচ্ছা আরজুকে দেখছি না যে?
সাবু - স্যার মাঝপথে এসে আরজু বলল তোরা যা। এরকম মাঝে মাঝেই করে আরজু।
লতিফ স্যার - কিন্তু কেন করে?
সাবু - এমনিই।
লতিফ স্যার - এমনিই মানে? ইচ্ছে করে? না কি কোনো সমস্যা আছে ওর?
সাবু - জানি না স্যার।
লতিফ স্যার - আচ্ছা। এই যে সোমেন, এদিকে শোনো, তোমার কী মনে হয় আরজু কি ইচ্ছে করেই স্কুল কামাই করছে?
সোমেন - স্যার, ওর যে কী হয়? হঠাৎ করে বলে আমি আর যেতে পারছি না, তোরা দাঁড়া। তখন ওয়ার্নিংবেল বেজে গেছে। আর কি দাঁড়াতে পারি? তাই তো চলে আসি, সেটাই ভালো না স্যার?
লতিফ স্যার - কোথায় যেন একটা সমস্যা মনে হচ্ছে।
মিঠু - স্যার ঐ ছেলেটার সাথে আমারও দেখা হয়েছে।
লতিফ স্যার - কোথায়?
মিঠু - ঐ যে পলাশতলীর আমবাগানের ওখানে বসে আছে। আমার সাথে নানান কথা।
লতিফ স্যার - নানা কথা? তাহলে স্কুলে এলো না কেন?
মিঠু - একসময় বলল তুমি কি স্কুলের দিকে যাবে? আমি বললাম না এখন বাজারে যাব। তারপর টিফিন পিরিয়ডের দিকে স্কুলের দিকে যাব।
লতিফ স্যার - তাহলে তো খুবই চিন্তার কথা। আচ্ছা ঐ আমবাগানে কি এখনও আছে?
সোমেন - মনে হয় এতক্ষণে বাড়ি চলে গেছে।
লতিফ স্যার - তোমরা চলো তো
সাবু - স্যার (ওদের চোখে মুখে অনিচ্ছা। হাওয়াই মিঠাইওয়ালা হেঁকে চলছে-হাওয়াই মিঠাই। লতিফ স্যার ওদের দুইজনকে নিয়েই রওয়ানা দেন।)
(আমবাগান। অসহায় আরজু বসে আছে। একা সে উঠে দাঁড়ায়। একটা পাখি ডাকছে। তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছে সে।)
আরজু - পাখি, একটু নিচে নাম না। তোমার সাথে কথা কই। আমাকে স্কুলে নিয়ে যাবে? সাবু, সোমেন ওরা কেউ নিয়ে গেল না। তুমি নিয়ে যাও না! তোমার ডানায় ভর করে চলে যাব। কী হলো? নেমে গেলে কেন? মেঘ আমায় নিয়ে যাও না। তোমার কোলে বসে চলে যাব স্কুলে। কী বলছ? ভিজে যাব? ভিজলাম। আবার শুকিয়ে যাব- তবুও তো স্যার বুঝবেন, ছোটো পাখি চন্দনা, এই যে শালিক আমাকে দেখতে পাচ্ছ না? আমি একলা বসে আছি। আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। আমার সাথে কথা বল না চন্দনা আমায় নিল না, মেঘ আমায় নিল না- শালিক আমার সাথে কথা বলে না।
(আরজু কাঁদতে থাকে। হঠাৎ উপস্থিত হয় লতিফ স্যার।)
লতিফ স্যার - আরজু, তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কী হয়েছে? তুমি স্কুলে যাও নি কেন?
সোমেন - কাঁদিস কেন? স্যারকে বল না। (আরজু কাঁদছেই)
লতিফ স্যার - কোনো ভয় নেই, বল।
আরজু - স্যার, আমি বেশি দূর হাঁটতে পারি না। পা দুটো অবশ হয়ে আসে।
লতিফ স্যার - তোমার বাবা-মাকে বল নি কেন?
আরজু - বলেছি- বাবা বলেন হাঁটাহাঁটি করলেই ঠিক হয়ে যাবে।
লতিফ স্যার - তোমার পা দুটো দেখি- এ তো রোগ, তোমার পা চিকন হয়ে গেছে।
আরজু - মা জানে, সেই ছোটোবেলায় কী যেন অসুখ হয়েছিল সেই থেকেই পাটা চিকন- মা বোঝে কিন্তু কাঁদে শুধু।
লতিফ স্যার - তোমরা খেয়াল কর নি?
সোমেন - না স্যার।
লতিফ স্যার - তোমাদের বন্ধু না?
সোমেন - জ্বী স্যার।
লতিফ স্যার - তোমার যদি এরকম হতো?
সোমেন - আমরা বুঝতে পারি নি স্যার। এরকম বুঝলে আমরা দুজনে ধরে এইভাবে নিয়ে যেতাম। (দুজনেই কাঁধে হাত দিয়ে ওকে তুলে ফেলে।)
লতিফ স্যার - বলো স্কুলে যাবে? না কি বাড়ি যাবে?
আরজু - স্কুলে স্যার। (ওদের কাঁধে হাত তুলে আরজু স্কুলে যায়।)
লতিফ স্যার - চলো। দেখি তোমার চিকিৎসার জন্য আমরা কী করতে পারি।
সেই ছেলেটি - 'সেই ছেলেটি' নামক এই লেখাটি একটি নাটিকা। এটি এ বইয়ের আর সব লেখার মতো নয়। এতে কয়েকজন বিশেষ বিশেষ জায়গায় থেকে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। এ ধরনের রচনা কেবল পড়ার জন্য নয়। এগুলো মঞ্চে অভিনয় করে লোককে দেখানো হয়। এ ধরনের লেখা আকারে বড়ো হলে তাকে বলে নাটক।
দৃশ্য - নাটক বা নাটিকায় বিষয়গুলোকে ঘটনাস্থল অনুসারে ভাগ করে নেওয়া হয়। এক-একটি ঘটনাস্থলকে 'দৃশ্য' বলা হয়। 'সেই ছেলেটি' নাটিকার তিনটি ঘটনাস্থলকে তিনটি দৃশ্যে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। ১ম দৃশ্য - গ্রামের পাশের রাস্তা। ২য় দৃশ্য - সাবু, আরজুদের স্কুল। ৩য় দৃশ্য আমবাগান।
মতলব - উদ্দেশ্য বা ফন্দি।
বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (শারীরিক ও মানসিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত) শিশুদের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি।
নাট্যকার মামুনুর রশীদ রচিত 'সেই ছেলেটি' একটি নাটিকা। নাটিকাটিতে একটি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (শারীরিক ও মানসিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত) শিশুর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। একই সাথে প্রকাশ পেয়েছে শিশুর প্রতি বড়োদের মমত্ববোধ। আরজু, সোমেন ও সাবু তিন বন্ধু একই স্কুলে একই শ্রেণিতে পড়ে। কিন্তু বিদ্যালয়ে হেঁটে আসতে আরজুর খুব কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে তার পা অবশ হয়ে আসে। বন্ধুদের সাথে সমান তালে চলতে পারে না। কখনো কখনো বসে পড়ে। বন্ধুরা আরজুর জন্যে আস্তে আস্তে হাঁটে। তাতে স্কুলে যেতে দেরি হয়ে যায় এবং ওরা শিক্ষকের কাছে বকুনি খায়। আসলে হয়েছিল কি, আরজু ছোটোবেলায় ভীষণ অসুখে পড়েছিল। তাতে তার পা সরু হয়ে যায়। কিন্তু আরজু জানে না কেন তার পা অবশ হয়ে আসে। তার মা জানেন আরজুর অসুখের কথা। তিনি কাঁদেন।
একদিন স্কুলে যাওয়ার পথে পা অবশ হয়ে গেলে আরজু বন্ধুদের স্কুলে চলে যেতে বলে। সে রাস্তার পাশে বসে থাকে। আইসক্রিমওয়ালা আসে, হাওয়াই মিঠাইওয়ালা আসে। সে তাদের সাথে কথা বলে। তারা চলে যায়। আরজু ভাবে পাখি কিংবা মেঘ তাকে যদি উড়িয়ে নিয়ে স্কুলে দিয়ে যেত!
এদিকে শিক্ষক লতিফ স্যার আরজুকে ক্লাসে না দেখে সোমেনদের কাছ থেকে ঘটনাটি জেনে সোমেনদের সঙ্গে নিয়ে আরজুর খোঁজে রওয়ানা হন। আরজুকে দেখে তিনি বুঝতে পারেন যে আরজুর পা অবশ হয়ে আসা একটা রোগ। তখন লতিফ স্যারের কথায় সোমেনদের মনে সহানুভূতি জাগে। তাদের সহায়তায় আরজু স্কুলে যায়।
মামুনুর রশীদ বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাট্যকার, অভিনেতা ও নির্দেশক। তিনি ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক হলো 'ওরা কদম আলী', 'ওরা আছে বলেই', 'ইবলিশ', 'গিনিপিগ' ইত্যাদি।
১. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য পোস্টার, প্ল্যাকার্ড, ব্যানার তৈরি করে র্যালির আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর কাজ)।
২. নাটিকাটি অভিনয় করে প্রদর্শনের ব্যবস্থা কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর কাজ)।
১. সেই ছেলেটি নাটিকায় দৃশ্য সংখ্যা কয়টি?
ক. দুইটি
খ. তিনটি
গ. চারটি
ঘ. পাঁচটি
২. আরজু তার বন্ধুদের সাথে স্কুলে যেতে যেতে বসে পড়ে কেন?
ক. সে স্কুলে যেতে চায় না
খ. স্যার তাকে বকুনি দিতে পারে
গ. তার স্কুল ফাঁকি দেওয়ার ইচ্ছা ছিল
ঘ. রোগের কারণে সে হাঁটতে পারে না
৩. 'মা বোঝে কিন্তু কাঁদে' কারণ-
ক. ছেলের পা চিকন হয়ে যাচ্ছে
খ. ছেলের পা একদিন পঙ্গু হয়ে যেতে পারে
গ. ছেলের পায়ের কোনো চিকিৎসা হচ্ছে না
ঘ. ছেলের এই অবস্থায় তিনি অসহায়
উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রেবেকা কাছের জিনিস দেখতে পায় কিন্তু দূরের জিনিস ঝাপসা দেখে। একদিন সে লক্ষ করল দূরের ঝাপসা জিনিস অর্ধেক দেখা যাচ্ছে আর অর্ধেক পুরো অন্ধকার। মাকে জানালে তিনি বললেন চোখে পানি দিলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। বরং অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে।
৪. রেবেকা কোন ধরনের শিশু?
ক. স্বাভাবিক
খ. পুষ্টিহীন
গ. সুবিধাবঞ্চিত
ঘ. বুদ্ধিহীন
৫. 'সেই ছেলেটি' নাটিকা অনুযায়ী রেবেকার প্রয়োজন-
i. মাতা পিতার সহানুভূতি
ii. সমাজের সহানুভূতি
iii. স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ধারণা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. i ও ii
গ. i ও iii
ঘ. ii ও iii
১. আবিদ স্যার ৭ম শ্রেণির ছাত্র রওশনের কাছে তার স্কুলে অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলে সে কিছু না বলে চুপ থাকে। শ্রেণির অন্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করলে তারা প্রায় একযোগে বলে স্যার, রওশন প্রায়ই স্কুল কামাই করে। শিক্ষক রওশনকে বলেন-আর কামাই করবে? কোনো উত্তর দেয় না রওশন। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে মেঝে খুঁড়তে থাকে। উত্তর না পেয়ে শিক্ষক রওশনকে অনেক বকা দেন। কয়েকদিন পর রওশনের বাবা আবিদ স্যারকে বলেন-স্যার, রওশনের স্নায়ু রোগ আছে। নিয়মিত স্কুল করলে ওর অসুখটা বেড়ে যায়। বকাঝকা করলে ওর স্কুলে আসা বন্ধ হয়ে যাবে।
ক. মিঠু আরজুকে কোথায় বসে থাকতে দেখেছে?
খ. আইসক্রিমওয়ালা আরজুকে স্কুল ফাঁকি দিতে নিষেধ করল কেন?- বুঝিয়ে লেখ।
গ. রওশন ও আরজুর মধ্যকার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।
ঘ. আবিদ স্যারের বিচার কাজটি লতিফ স্যারের তুলনায় কতটুকু যৌক্তিক হয়েছে? তা মূল্যায়ন কর।
আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি এই বাংলাদেশ বহু জাতি, বহু ভাষা ও বহু সংস্কৃতির একটি দেশ। এখানে প্রধান জনগোষ্ঠী বাঙালির পাশাপাশি রয়েছে প্রায় অর্ধশত জাতিসত্তার মানুষ। দেশের প্রধান ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার পাশাপাশি রয়েছে অনেক ভাষা এবং ঐসব জাতিগোষ্ঠীর নানা বর্ণের বিচিত্র সংস্কৃতিও। তারপরও আমরা সবাই জাতীয়তার পরিচয়ে এক এবং দেশকে ভালোবাসার ক্ষেত্রেও ঐক্যবদ্ধ। বৈচিত্র্যের মধ্যেও এই যে একতার শক্তি, এটিই আমাদের বাংলাদেশকে সুন্দর ও বর্ণময় করে তুলেছে।
বাঙালি ছাড়া বাংলাদেশে বসবাসরত অন্যান্য জাতিসত্তার সংখ্যা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। তবে সাধারণভাবে এই সংখ্যা ৪৬টি বলে অনুমিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের বিভিন্ন পাহাড়ি জনপদ ছাড়াও দেশের সমতলভূমি যেমন কক্সবাজার, পটুয়াখালি, বরগুনা, ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর ও সিলেট অঞ্চলে প্রধানত এদের বসতি। এইসব জনগোষ্ঠী শত শত বছর ধরে এই ভূখণ্ডে বসবাস করছে। তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর কাছে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি খুবই প্রিয়।
বাংলাদেশে যেসব সংখ্যাস্বল্প জাতিসত্তার বাস তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাঁওতাল, মণিপুরি, খাসি, স্রো, রাখাইন, হাজং, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, কোচ, পাহাড়িয়া, রাজবংশী, মালো, ওঁরাও ইত্যাদি। এদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতির পরিচয় সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।
মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত চাকমাদের প্রধান বসতি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায়। নিজেদের মধ্যে তারা 'চাঙমা' নামে পরিচিত। তারা আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের নিজস্ব হরফও আছে। চাকমারা পিতৃতান্ত্রিক। পিতাই পরিবারের প্রধান। চাকমা সমাজের প্রধান হলেন রাজা। গ্রামের প্রধান হলেন কারবারি। গ্রামের যাবতীয় সমস্যা তিনিই নিষ্পত্তি করেন। চাকমারা প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তবে তার পাশাপাশি এখনও তারা কিছু কিছু প্রকৃতিপূজাও করে থাকে। চাকমা পুরুষেরা 'ধুতি' ও মহিলারা 'পিনন' পরিধান করে থাকে। পুরুষেরা নিজেদের তাঁতে তৈরি 'সিলুম' (জামা) পরে। মেয়েরা 'খাদি'কে ওড়না হিসেবে ব্যবহার করে।
চাকমাদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ, মাংস ও শাক-সবজি। চাকমা-জীবনের নানা পর্যায়ে বিভিন্ন লৌকিক আচার অনুষ্ঠান থাকে। বিয়ের সময় ছেলের অভিভাবককে ঘটকসহ কনের বাড়িতে কমপক্ষে তিনবার যাওয়া-আসা করতে হয়। প্রতিবার চুয়ানি, পান-সুপারি ও পিঠা নিয়ে যেতে হয়। বিজু উৎসব চাকমাদের একটি প্রধান উৎসব। চৈত্রের শেষ দুইদিন 'ফুলবিজু' ও 'মূলবিজু' এবং পহেলা বৈশাখকে 'গ্যাপৰ্য্যা' বলে আখ্যায়িত করে থাকে তারা। লোকনৃত্যগীত হিসেবে 'জুমনাচ' ও 'বিজুনাচ' বেশ জনপ্রিয়।
গারো জনগোষ্ঠীর প্রধান বসতি ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও সিলেট অঞ্চলে। মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত গারোরা মাতৃসূত্রীয়। মেয়েরা পরিবারের সম্পত্তির মালিক হয়। বিবাহের পর বর স্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে বসবাস করে থাকে। সন্তান-সন্ততিরা মায়ের পদবি ধারণ করে। তবে পরিবার, সমাজ পরিচালনা ও শাসনে পুরুষেরাই দায়িত্ব পালন করে থাকে। একই গোত্রে বিবাহ গারো সমাজে নিষিদ্ধ। গারোদের নিজস্ব ধর্ম আছে। এটি এক ধরনের প্রকৃতি-পূজা। গারোরা প্রধানত কৃষিজীবী। পাহাড়ে বসবাসকারীরা জুম চাষ করে। আর সমতলভূমির গারোরা নারী ও পুরুষ একসাথে সাধারণ নিয়মে কৃষিকাজ করে। গারোরা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি জীবনের নানা পর্যায়ে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। অলঙ্কারও ব্যবহার করে থাকে। গারো সংস্কৃতিতে গীতবাদ্য ও নৃত্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের নিজস্ব কিছু বাদ্যযন্ত্রও আছে। ফসল বোনা, নবান্ন, নববর্ষ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন হয়। 'ওয়ানগালা' গারোদের একটি জনপ্রিয় উৎসব।
মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত মারমাদের প্রধান বসতি পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে। মারমা ভাষাও মঙ্গোলীয় ভাষা পরিবারের। তাদের নিজস্ব বর্ণমালাও আছে। মারমারা প্রাচীনকাল থেকেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তারা বিয়ের সময় ধর্মীয় ও লোকাচার মিলিয়ে নানা অনুষ্ঠান পালন করে। নিজেদের গোত্রে বিবাহকে মারমা সমাজে উৎসাহিত করা হয়। মারমারা পিতৃতান্ত্রিক। সম্পত্তির উত্তরাধিকারে ছেলে ও মেয়েদের সমান অধিকারের কথা বলা আছে। তবে পরিবার ও সমাজজীবনে পুরুষেরই প্রাধান্য থাকে। বিয়ের পর নারী-পুরুষ ইচ্ছে করলে মা-বাবার বাড়ি কিংবা শ্বশুরবাড়িতে স্থায়িভাবে বসবাস করতে পারে। মারমাদের সামাজিক শাসনব্যবস্থায় রাজা প্রধান। মারমারা জুম চাষ করে এবং বনজ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহ করে।
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও মারমারা এখনও বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা এবং নানা আচার-অনুষ্ঠানাদি পালন করে। তাদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব হলো নববর্ষে সাংগ্রাই দেবীর পূজা এবং এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংগ্রাই উৎসব তিন দিন ধরে চলে।
মণিপুরিদের আদি নিবাস ভারতের মণিপুর রাজ্য। এদের মধ্যে কোনো কোনো সম্প্রদায়ের নিজস্ব বর্ণমালাও আছে। মণিপুরিরা যেখানেই বসতি স্থাপন করে সেখানে কয়েকটি পরিবার মিলে গড়ে তোলে পাড়া। প্রতিটি পাড়াতেই থাকে দেবমন্দির ও মণ্ডপ। ঐ মন্দির ও মণ্ডপকে ঘিরেই আবর্তিত হয় ঐ পাড়ার যাবতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ড। মণিপুরি সমাজে পাড়া বা গ্রাম ও 'পানচায়' বা পঞ্চায়েতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মণিপুরি জনগোষ্ঠী সাতটি গোত্রে বিভক্ত। মণিপুরিদের প্রাচীন ধর্মের নাম 'আপোকপা'। তবে মণিপুরিদের অধিকাংশই এখন সনাতন ধর্মের চৈতন্যমতের অনুসারী। মণিপুরিদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। সনাতন ধর্মাবলম্বী মণিপুরিদের প্রধান উৎসব রাস উৎসব, রথযাত্রা ইত্যাদি। রাস উৎসব উপলক্ষ্যে রাসনৃত্য ও মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। মণিপুরিরা প্রধানত কৃষিজীবী। ভাত, মাছ, শাক-সবজি মণিপুরিদের প্রধান খাদ্য। মণিপুরি পুরুষেরা সাধারণত ধুতি, গামছা, জামা ইত্যাদি পরিধান করে। আর মেয়েরা পরে নিজেদের তৈরি বিশেষ ধরনের পোশাক।
পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি, রামগড়, রাঙামাটি, কাপ্তাই এবং চট্টগ্রাম জেলা, বৃহত্তর কুমিল্লা, নোয়াখালি ও সিলেট অঞ্চলে বসবাসকারী ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী মঙ্গোলীয় মহাজাতির অংশ। তাদের ভাষার নাম 'ককবরক'। এদের নিজস্ব কোনো বর্ণমালা নেই। ত্রিপুরা সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। ছেলেরাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। ত্রিপুরারা বর্তমানে সাধারণভাবে সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। কিন্তু তারা এখনও তাদের প্রাচীন লোকজ ধর্মের নানা দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি করে।
ত্রিপুরা মেয়েরা কাপড় বয়নে খুবই দক্ষ। তারা নিজেদের পরনের কাপড় নিজেরাই তাঁতে তৈরি করে। পুরুষেরা পরিধান করে নিজেদের তৈরি গামছা ও ধুতি। ত্রিপুরারা কৃষিজীবী। তারা পাহাড়ে জুম চাষ করে। ত্রিপুরাদের সংগীত ও নৃত্য খুবই সমৃদ্ধ। তাদের মধ্যে বিভিন্ন সংগীতের প্রচলন যেমন আছে, তেমনি আছে নানা প্রকারের নৃত্যও। ত্রিপুরাদের প্রধান উৎসব নববর্ষ বা বৈসু। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর 'বৈসু', মারমাদের 'সাংগ্রাই' ও চাকমাদের 'বিজু' উৎসবের প্রথম অক্ষর নিয়ে 'বৈসাবি' উৎসব এখন নববর্ষ উপলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতীয় উৎসব।
সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর লোক প্রধানত উত্তরবঙ্গ ও সিলেটের চা বাগানে বসবাস করে। তাদের ভাষা অস্ট্রিক পরিবারের। সাঁওতাল সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। সম্পত্তির মালিকানায় এবং সমাজ ও পরিবারে পুরুষই প্রধান। সাঁওতালদের নিজস্ব ধর্ম আছে। কিন্তু কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই। পেশার দিক থেকে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত - কৃষক ও শ্রমিক। অনেকের জন্যে কৃষি যেমন প্রধান জীবিকা তেমনি অনেকে আবার শ্রমিক হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে থাকে। ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে সাঁওতালদের সংগ্রামী ভূমিকা, বিশেষ করে 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' ও 'নাচোল কৃষক বিদ্রোহ' ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে।

সাঁওতালরা খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। বাড়িঘর লেপে মুছে পরিষ্কার রাখা হয় এবং দেয়ালে নানা রঙ দিয়ে ছবি আঁকা হয়। 'সোহরাই' হচ্ছে সাঁওতাল সমাজের শ্রেষ্ঠ উৎসব। এটা অনেকটা পৌষ-পার্বণের মতো। সাঁওতাল নৃত্যে মেয়ে-পুরুষ দলবদ্ধ হয়ে নাচে। তাদের ঝুমুর নাচ খুবই জনপ্রিয়।
বাংলাদেশের এইসব ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তার জীবন ও সংস্কৃতি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে-বর্ণিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করেছে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নেও রয়েছে তাদের বিরাট অবদান। তারা আজ জাতীয় মূলধারারই অংশ।
(সংক্ষেপিত)
সংখ্যাম্বল্প জাতিসত্তা - বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ হচ্ছে বাঙালি। বাঙালি ছাড়া আরও কিছু জনগোষ্ঠী বা জাতি আছে, যারা ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতির দিক থেকে বাঙালিদের মতো নয়। তাদের সংখ্যা বাঙালিদের তুলনায় কম। যেমন: চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, হাজং, ত্রিপুরা ইত্যাদি।
সংস্কৃতি - ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের আত্মপরিচয় পাওয়া যায় এমন সব বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় সংস্কৃতি। বাঙালির কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলোর দ্বারা বাঙালিকে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী থেকে আলাদা করা যায়। তেমনি ক্ষুদ্র জাতিসমূহের সংস্কৃতিও আলাদা আলাদা। তবে নাগরিকত্বের পরিচয়ে বাংলাদেশের সকলেই এক ও অভিন্ন।
আর্যভাষা - দুনিয়ার একটি প্রধান ভাষাগোষ্ঠীর নাম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী। তার একটি শাখার নাম আর্য ভাষা। এই আর্য ভাষা থেকে বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া, চাকমা প্রভৃতি ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।
পিতৃতান্ত্রিক পরিবার - মানব সমাজে দু'রকমের পরিবার প্রথার সৃষ্টি হয়েছে: (ক) পিতৃতান্ত্রিক, (খ) মাতৃতান্ত্রিক। পরিবারের প্রধান নেতৃত্ব, অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও সম্পত্তি যদি পুরুষের হাতে থাকে তাহলে সেরকমের পরিবারকে বলা হয় পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। আর যে পরিবার প্রথায় উক্ত নেতৃত্ব ও ক্ষমতা নারীর হাতে থাকে, তাকে বলা হয় মাতৃতান্ত্রিক। বাঙালিদের মতো চাকমাদের পরিবার পিতৃতান্ত্রিক। তবে একালে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারেও পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের প্রভাব পড়েছে।
খাদি - হাতে কাটা (মেশিনে নয়) সুতা দিয়ে তৈরি কাপড়।
লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান - স্থান ও জাতি বিশেষের ঐতিহ্যগত আচার-অনুষ্ঠান যার মধ্যে বর্তমান নাগরিক রুচির প্রভাব পড়ে নি, তাকে লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান বলা হয়।
মাতৃসূত্রীয় পরিবার- - কিছু সমাজ আছে যেখানে পুরুষগণ সমাজ পরিচালনা ও শাসনের অধিকারী হলেও নারীদের পরিচয়েই পরিবার পরিচিত হয়। এ ধরনের পরিবারকে মাতৃসূত্রীয় পরিবার বলে। যেমন- গারো পরিবার।
পদবি - উপাধি, যা নামের শেষে যোগ করে বংশ পরিচয় দেওয়া হয়। পদবি বলতে কর্মক্ষেত্রে স্তর বা মর্যাদাও বোঝায়।
জুম - পাহাড়ে চাষাবাদের বিশেষ পদ্ধতি।
মঙ্গোলীয় ভাষাগোষ্ঠী - একটি ভাষাগোষ্ঠী; এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রতিটি ভাষার আলাদা রূপ ও বৈশিষ্ট্য আছে।
মণ্ডপ - পূজা বা সভা-সমিতির জন্য ছাদযুক্ত চত্বর।
বয়ন - বোনা।
বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।
বাংলাদেশে মূল জনগোষ্ঠী হচ্ছে বাঙালি জাতি। বাঙালি ছাড়াও এদেশে আরও অনেক জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বাস করে। তাদের মধ্যে আছে চাকমা, গারো, মারমা, মণিপুরি, ত্রিপুরা, সাঁওতাল প্রভৃতি জনগোষ্ঠী।
এই জাতিগোষ্ঠীর প্রত্যেকটিরই রয়েছে স্বতন্ত্র পরিচয়, নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবনাচার। তাদের মধ্য থেকে কয়েকটি সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। চাকমা, গারো, মারমা, মণিপুরি, ত্রিপুরা ও সাঁওতালদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত এই আলোচনা বৃহত্তর জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে বলে ধারণা করা যায়।
বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও জীবনাচার আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে, করেছে বৈচিত্র্যময় ও বর্ণিল। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।
বাংলাদেশে মণিপুরি সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ কবি ও প্রাবন্ধিক এ. কে. শেরাম। তাঁর জন্ম ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে হবিগঞ্জে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো: 'বসন্ত কুন্নি পালগী লৈরাং', 'মণিপুরি কবিতা', 'চৈতন্যে অধিবাস', 'মনিদীপ্ত মণিপুরি ও বিষ্ণুপ্রিয়া বিতর্ক' ইত্যাদি।
ক. তোমার এলাকার বিভিন্ন লোকজ-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিচয় দিয়ে একটি রচনা লেখ (একক কাজ)।
১. ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর উৎসব কোনটি?
ক. সাংগ্রাই
খ. বিজু
গ. বৈসু
ঘ.
সোহরাই
২. বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতিসত্তা জাতীয় মূলধারারই অংশ কারণ, তারা-
i. আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে
ii. জাতীয় সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে
iii. ধর্মীয় দিক থেকেও তারা গুরুত্বপূর্ণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. iii ও i
ঘ. i, ii ও iii
উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
বাবার চাকরির সুবাদে সুমি সিলেটের একটি স্কুলে ভর্তি হয়। সেখানে লুসি দাড়িং নামে একটি মেয়ের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়। কথা প্রসঙ্গে সুমি জানতে পারে 'দাড়িং' লুসির মায়ের পদবি। শুনে তার কাছে অদ্ভুত লাগে যে বিয়ের পর লুসির বাড়িতেই তার বর চলে আসবে।
৩. উদ্দীপকে বাংলাদেশের জাতিসত্তা সম্পর্কিত এই রচনায় কোন জাতিসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়?
ক. চাকমা
খ. মারমা
গ. গারো
ঘ. সাঁওতাল
8. উদ্দীপকের জাতিসত্তা আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ, তারা আমাদের-
i. সংস্কৃতির ধারক
ii. অবিচ্ছেদ্য অংশ
iii. ঐতিহ্যকে ধারণ করেছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
১। বাহার তার বন্ধু সঞ্জীবের সাথে একটি পার্বত্য অঞ্চলে বেড়াতে যায়। সেখানে গিয়ে সে জানতে পারে স্থানীয় লোকজন সবাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, পিতৃতান্ত্রিক। তারা দেব-দেবীর পূজা করে এবং নববর্ষ এলে সাংগ্রাই উৎসব পালন করে। সেখানে কয়েকদিন থাকার পর তারা অন্যত্র বেড়াতে যায়। সেখানকার সমাজের প্রধান হলেন রাজা। গ্রামের প্রধান হলেন কারবারি। সেখানে পুরুষেরা ধুতি ও মহিলারা 'পিনন' পরিধান করে থাকে। পুরুষেরা নিজেদের তৈরি 'সিলুম' পরে। মেয়েরা খাদিকে ওড়না হিসেবে ব্যবহার করে।
ক. চাকমারা পহেলা বৈশাখকে কী বলে আখ্যায়িত করে?
খ. পঞ্চায়েতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেন?
গ. উদ্দীপকের প্রথম স্থানটি এই রচনার কোন জাতিসত্তাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "বাহার ও তার বন্ধু শেষে যেখানে বেড়াতে গেল তা বাংলাদেশের একটি জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে।"-উদ্দীপক ও রচনার আলোকে বিশ্লেষণ কর।
common.read_more